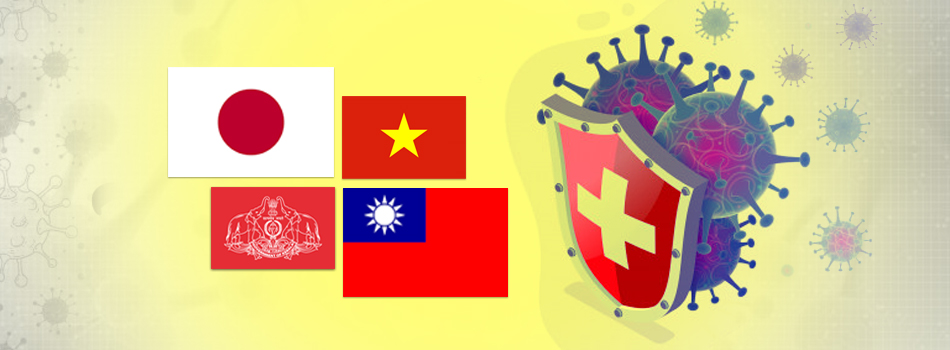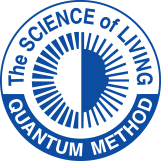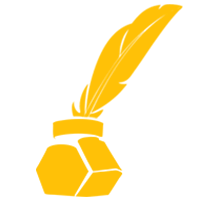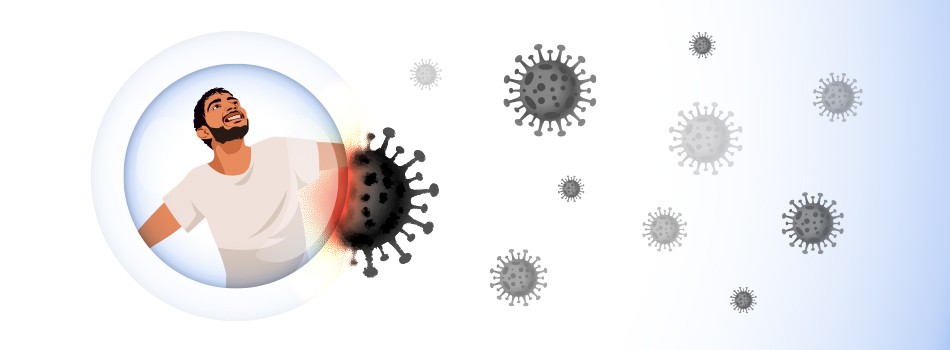
রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা : কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মূল হাতিয়ার
published : ২৯ মে ২০২০
১.
চীন থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১১ মার্চ ২০২০ মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রথম নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয় ৮ মার্চ ২০২০। চীন সরকার ডিসেম্বর ২০১৯-এর শেষার্ধে প্রথমবারের মতো জানায় যে, চীনে একটি মারাত্মক ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। এর আগপর্যন্ত এ নভেল ভাইরাসটি গোটা বিশ্বে অজানাই ছিল। ১১ ফেব্রুয়ারি International Committee on Taxonomy of Viruses এই ভাইরাসটির নামকরণ করে ‘SARS-CoV-2’ (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) এবং WHO এই ভাইরাসবাহিত রোগটির নামকরণ করে ‘COVID-19’ (Corona Virus Disease 2019)।
নামকরণের পরপরই কোভিড-১৯ আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথন, আলাপচারিতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য প্রবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দল ভাইরাসটির জিনোম তথ্য ও মলিকিউলার মেকানিজম উন্মোচন এবং টিকা-অ্যান্টিভাইরাল আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। বহুল আলোচিত SARS-CoV-2 প্রধানত ক্ষুদ্র এক টুকরো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল (RNA), যাকে আবৃত করে রাখে প্রোটিন ক্রাউনযুক্ত একটি লিপিড কোট। চীনের উহানে অবস্থিত একটি সী-ফুড বাজারে এই নভেল করোনাভাইরাসটি উদ্ভূত হয়, যা সেখানেই কিছু মানুষকে প্রথমে সংক্রমিত করে।
করোনাভাইরাস মহামারী বিশ্বকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন করেছে। এই প্রবন্ধটি লেখাকালীন সময়ে বিশ্বের ২১৩টি দেশে মারাত্মক সংক্রামক এ ভাইরাসটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ লক্ষাধিক এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষাধিক। এত মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই সবার মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশসহ বহু দেশে এর সংখ্যা তাত্পর্যপূর্ণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্যদের মতো আমাদের সরকারও এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভাইরাসের বিস্তার কমাতে সরকার অফিস-আদালত বন্ধ ঘোষণা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শাটডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে মেলামেশার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তবে অনেকেই এই নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করে নি। সম্প্রতি খাবারের দোকান ও বিপণি বিতান খুলে দেয়ার ফলে পরিস্থিতি আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাইরাসের প্রকোপ ও সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে আতঙ্ক।
করোনা আতঙ্ক যতটা আলোচিত হয়েছে, ভাইরাস প্রতিরোধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার গুরুত্ব তেমনটি আলোচিত হয় নি। SARS-CoV-2 তে আক্রান্ত কিছু মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও আক্রান্তের ৮০ ভাগের বেশি মানুষ তেমনভাবে অসুস্থ হন নি। ঠিক কী কারণে কিছু মানুষের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং বাকিদের দেহে রোগটি লক্ষণহীন তা জানা যায় নি। তবে এটি ব্যক্তির দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে। কারো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার শক্তি বা দুর্বলতা নির্ভর করে ভাইরাসের ধরন, পরিমাণ এবং শরীরে কোন পথে প্রবেশ করেছে তার ওপর। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, পূর্বের যেসব মহামারীর টিকা অনাবিষ্কৃত ছিল, সেসব মহামারীর মোকাবেলা মানুষ এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েই সফলভাবে করেছে। সুতরাং, টিকা আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই নভেল করোনাভাইরাস প্রতিহত করতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভূমিকাই হবে মুখ্য। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই এই ঘাতক জীবাণু থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং কার্যকরী চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবেও সহায়ক হবে।
২.
করোনাভাইরাস সাধারণত মানুষের নাক বা মুখের মাধ্যমে রেসপিরেটরি ড্রপলেটের সাথে প্রবেশ করে এবং নাকের লাইনিং-এর কোষ ও ফুসফুসের কোষগুলোর সংস্পর্শে আসে। স্পাইক প্রোটিনের সাহায্যে ভাইরাসটি একটি কোষকে আঁকড়ে ধরে তাকে সংক্রমিত করে। ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও অন্ত্রের কোষপৃষ্ঠে প্রদর্শিত Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE-2) নামক রিসেপ্টরের সাথে স্পাইক প্রোটিন সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্তির মাধ্যমেই ভাইরাস তার জিনের উপাদান দেহকোষে প্রবেশ ঘটায় এবং কোষের সমস্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে নতুন ভাইরাসের জন্ম দেয় ও পরবর্তী সংক্রমণ ছড়ানোর ব্যবস্থা করে। এদিকে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিন্তু বিনা যুদ্ধে ভাইরাসের এই সংক্রমণকে ছড়াতে দেয় না। রোগ প্রতিরোধী যোদ্ধা কোষগুলো অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সংক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দেয়। যে যোদ্ধা কোষগুলি প্রতিরোধী যুদ্ধে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা হলো গ্র্যানুলোসাইট, ম্যাক্রোফাজ এবং ন্যাচারাল কিলার (এনকে) সেল। তাদের এ প্রতিরোধকে সহজাত ইমিউন প্রতিক্রিয়া (innate immune response) বলে। দেহকোষ থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত এনজাইম, আক্রান্ত কোষ থেকে নিঃসৃত ইন্টারফেরন নামক এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন এবং অন্যান্য সিগন্যালিং অণু ভাইরাস প্রতিরোধে তৎপর হয়ে ওঠে। এনকে সেল সুনির্দিষ্টভাবে ভাইরাস-আক্রান্ত কোষের কোষপৃষ্ঠে প্রকাশিত স্ট্রেস প্রোটিনকে শনাক্ত করে ঐ কোষগুলিকে মেরে ফেলে। সহজাত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এভাবেই ভাইরাসের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই বিপুল সংখ্যক জনগণের মাঝে কোভিড-১৯ এর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
অপরপক্ষে SARS-CoV-2 বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চায় এবং এড়াতে সক্ষম হলেও পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত হয় না। কিছু সময় পর দ্বিতীয় দফায় আরেকটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয় যাকে বলা হয় অভিযোজিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা (adaptive immune response)। সংক্রমণের মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন সাইটোটক্সিক টি-সেলের (cytotoxic T-cell) সংখ্যা ও কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সাইটোটক্সিক টি-সেল আক্রান্ত কোষকে শনাক্ত করার জন্যে প্রহরীর মতোই টহল দেয়। শনাক্ত করামাত্র টি-সেলটি আক্রান্ত কোষের সাথে সংযুক্ত হয়ে কোষ ঝিল্লিতে ছিদ্র তৈরি করে বিষাক্ত পদার্থ প্রেরণ করে। ফলে আক্রান্ত কোষটি অভ্যন্তরীণ ভাইরাসসহ ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে, বি সেল (B-cell) অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা বিশেষত ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়। ফলে ভাইরাস তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আক্রমণকারী জীবাণুকে স্মরণে রাখে এবং পরবর্তীতে একই জীবাণু যদি পুনরায় আক্রমণ করে, দেহ তৎক্ষণাৎ একে দমনে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সক্ষম হয়।
৩.
এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩৮ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় ৫৫০। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় দেড় লক্ষ ও ৬০ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় ৪,৪০০ ও ১,২০০। তুলনামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার অনেক বেশি। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ লক্ষের বেশি এবং মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় এক লক্ষ মানুষ। স্পেন, ইটালি, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় দেশগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা ২-৩ লক্ষ এবং মৃত্যুবরণ করেছে ২৭,০০০-৩৭,০০০ জনের মতো। আশ্চর্যজনকভাবে, বাংলাদেশসহ ঘনবসতিপূর্ণ উপমহাদেশীয় দেশগুলোতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক কম।
মৃতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় আমাদের মানসিক চাপও হয়তো-বা কিছুটা কম। তবে এই পরিস্থিতি এই প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে যে, দরিদ্র ঘনবসতিপূর্ণ উপমহাদেশীয় দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলোতে কোভিড কেসের সংখ্যা এত বেশি কেন?
এ প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর পাওয়া সহজ নয় কেননা উপমহাদেশীয় দেশগুলোর ব্যবহার্য সম্পদ এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। আরো বেশি সংখ্যক টেস্ট সম্পন্ন হলে করোনা আক্রান্ত রোগী ও মৃতের সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পেত কিন্তু সে সংখ্যাও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম হতো বলেই অনেকের বিশ্বাস। এই চিত্র এই ধারণার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এই অঞ্চলের জনগণের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত দেশগুলোর জনগণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে বেশি শক্তিশালী।
৪.
পূর্বের কিছু গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, শিশুরা রোগ প্রতিরোধে ভালো সক্ষমতা অর্জন করে যদি তাদেরকে তুলনামূলক অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে লালনপালন করা হয়। এই ধারণাটি হাইজিন হাইপোথিসিস নামে পরিচিত। ধারণাটি ব্যাখ্যা করে যে শিশুর প্রারম্ভিক জীবনে বিভিন্ন জীবাণুর সংস্পর্শ তাদের ক্রমবর্ধমান রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দেয়।
শৈশব থেকেই বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোর মানুষ ব্যাপকভাবে জীবাণুর সংস্পর্শ পায়, যা হয়তো তাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসসহ অন্যান্য জীবাণুর সংস্পর্শ দেহে প্রচুর পরিমাণ মেমোরি টি-সেল পুঞ্জীভূত করতে ভূমিকা রাখে। এই মেমোরি টি-সেলগুলো বাইরে থেকে আগত যে-কোনো জীবাণু মোকাবেলায় সদাপ্রস্তুত থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার এই দিকটিই উপমহাদেশীয় অঞ্চলের মানুষকে অতি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা উন্নত দেশের মানুষের তুলনায় বাড়তি সুবিধা দেয়।
একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভারতীয়দের শরীরে ন্যাচারাল কিলার সেলের সংখ্যা বেশি থাকে, যা যে-কোনো সংক্রমণকে শুরুতেই শনাক্ত এবং নিরসন করতে সক্ষম। বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সপক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আপাতত আমাদের কাছে নেই। তবে উপর্যুক্ত ভারতীয় গবেষণালব্ধ তথ্য বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর উন্নত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ধারণাটিকে আংশিকভাবে হলেও সমর্থন করে।
কেন কিছু মানুষ এ ভাইরাসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার অন্যরা মোটেও অসুস্থ হয় না—এর নেপথ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জেনেটিক ফ্যাক্টর-এরও ভূমিকা থাকতে পারে। HLA (human leukocyte antigen) এবং KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors)-এর মতো রোগ প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী জিনগুলোর কার্যকারিতা এই তারতম্যে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে—ভারতীয়রা, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন HLA এবং KIR জিন অর্জন করে যা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদেরকে সহায়তা দান করে। এই জিনগুলো প্রারম্ভিক পর্যায়ে সংক্রমণ শনাক্ত এবং প্রতিহত করতে সক্ষম, যা এই অঞ্চলের মানুষকে জিনগত সুবিধা দিয়ে থাকে।
বাংলাদেশ কলেরাপ্রবণ একটি দেশ; আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, এদেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে কলেরার শক্তিশালী সিলেক্টিভ প্রেশার বিদ্যমান। এ গবেষণালব্ধ ফল অনুযায়ী কলেরা NF-κB এবং inflammasome signaling-এর উপর সিলেক্টিভ প্রেশার প্রদান করে। এ ধরনের সিগনালিং সহজাত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থারই অংশ। এ সকল বৈজ্ঞানিক উপাত্ত জীবাণু মোকাবেলায় এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জিনের সংশ্লিষ্টতার দিকে আলোকপাত করে। আমাদের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টগুলো শনাক্তকরণে বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন, কেননা এই ভ্যারিয়েন্টগুলোই হয়তো ভাইরাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখছে।
৫.
পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাস এপিজেনেটিক (epigenetic) ফ্যাক্টরকে প্রভাবিত করে, যা বাংলাদেশসহ অনেক এশীয় দেশের জন্যে কল্যাণকর। এই এলাকার মানুষ খাদ্যে নানা প্রকারের মসলা ব্যবহার করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মসলার গুরুত্ব সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা মুদ্রিত হয়েছে। মসলার মধ্যে সবচাইতে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে হলুদ, যা আমরা দৈনন্দিন খাদ্যপ্রস্তুতিতে ব্যবহার করে থাকি। হলুদে ‘কারকিউমিন’ নামক একধরনের উপাদান থাকে, এটি রোগ প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোষকে সক্রিয় করে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি হলুদ এই কোষগুলোকে জীবাণুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক লড়াই করার জন্যেও প্রস্তুত করে। এভাবেই আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বলিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে হলুদ অবদান রাখে। এ-ছাড়াও মসলা হিসেবে রসুন, আদা, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, ধনে, জিরা, কালোজিরা, সরিষা ইত্যাদি আমাদের দেশে হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়। এই মসলার অনেকগুলোতেই প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং জৈবিকভাবে কার্যকরী উপাদান আছে। এই মসলাগুলোর সক্রিয় উপাদানের জীবাণুনাশক কার্যকারিতাই তো পূর্বে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন প্রকার মসলা একক বা সম্মিলিতভাবে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।
৬.
কোনো কোনো ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিছু কোভিড-১৯ রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাকোষের অতি সক্রিয়তা এবং এই কোষ দ্বারা নিঃসৃত সাইটোকাইনের অতি নিঃসরণ ঘটে। নিজ দেহকোষের বিরুদ্ধে এ সাইটোকাইনগুলোই শুরু করে দেয় মাত্রাতিরিক্ত যুদ্ধ। ফলে রোগীর 'সাইটোকাইন স্ট্রর্ম' সিন্ড্রোম দেখা দেয়। এই রোগীদের অধিকাংশই ষাটোর্ধ্ব—যারা ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা বা উচ্চরক্তচাপে ভুক্তভোগী। সাধারণত সাইটোকাইন স্টর্ম সিন্ড্রোম দেখা দেয় যখন ফুসফুসে অসংযত যোদ্ধা কোষগুলি লাগামহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রদাহ সৃষ্টি করে। ভাইরাস এবং যোদ্ধাকোষগুলির হিংস্র লড়াইয়ের পর ফুসফুসে মৃতকোষের স্তূপ জমতে থাকে। এর ফলে শ্বাসনালীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে অক্সিজেনের প্রবাহ হ্রাস পায়। যার কারণে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রচণ্ডভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দেহ এর ধকল নিতে না পারায় ধীরে ধীরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কার্যকারিতা হারায় এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার যথাযথ সক্রিয়তা যেমন জীবন বাঁচায়, তেমনি দীর্ঘমেয়াদী ও অতিমাত্রার সক্রিয়তা প্রাণনাশের কারণও হয়ে থাকে।
৭.
বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ও মৃতের হার কম হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অবশ্যই অপর্যাপ্ত টেস্ট। এখানকার উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং কম সংক্রমণও কম মৃত্যুহারের নেপথ্য কারণ হয়ে থাকতে পারে। এ-ছাড়া, বিসিজি টিকারও ভূমিকা থাকতে পারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় রেখে করোনা প্রকোপ কমানোয়। তবে বাংলাদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় কারণ হলো আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অধিক কার্যকারিতা। এই ধারণা মোটেই অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তাছাড়া এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের মানসিক সক্ষমতাও প্রবল। সুতরাং করোনা মহামারী প্রতিহতে আমাদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা যেমন পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তেমনি একে সহায়তা করছে মানসিক সক্ষমতাও।
২৭ মে ২০২০
লেখক

ড. মো: আনোয়ারুল আজীম আখন্দ
অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়