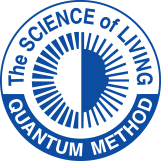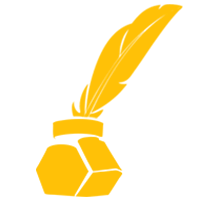টাকার মোহের কাছে নয়, আবিষ্কারের কাজে যিনি নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন
published : ২৫ নভেম্বর ২০২০
২৩ নভেম্বর, ২০২০ ছিল বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ৮৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী। আর ৩০ নভেম্বর তার জন্মদিন। ১৮৫৮ সালের এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মহান এই বিজ্ঞানীকে নিয়েই এবারের আর্টিকেল-
যেদিন আমার ন্যায্য বেতন পাব সেদিনই নেব
রাত ১১টা। এখনো বাড়ি ফেরেন নি স্বামী জগদীশচন্দ্র বসু। বাড়িতে অপেক্ষা করছেন স্ত্রী অবলা বসু। স্বামী ইদানীং প্রায়ই দেরি করে ফিরছেন। অপেক্ষা করাটা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার কথা। কিন্তু তারপরও বার বার চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে।
এদিকে জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণাগারে কী যেন করছেন গভীর মনোযোগে। বৈদ্যুতিক তারের সাথে তার জোড়া দিচ্ছেন। ভোল্টেজ মাপছেন। আবার খুলে ফেলছেন। তিনি চাইছেন তারবিহীন এক প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে। তথ্য আদান-প্রদান হবে, কিন্তু কোনো তারের সংযোগ থাকবে না। বিষয়টি যতবার ভাবছেন ততবারই তিনি শিহরিত হচ্ছেন।
যেখানে তিনি কাজ করছেন এটিকে গবেষণাগার বললে ভুল হবে। ২৪ বর্গফুটের ছোট্ট একটি ঘর। ঢোকার আগেই শেষ হয়ে যায়। শৌচাগারের পাশে বলে মাঝে মাঝে উৎকট গন্ধও আসছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিত্যক্ত এই ঘরটি বরাদ্দ পেয়েছেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র। খানিকটা মেরামত করে এটাকেই কোনোমতে কাজের জায়গা বানিয়ে নিয়েছেন। কলকাতার স্বনামধন্য এই কলেজটিতে আলাদা গবেষণাগার রয়েছে, কিন্তু সেখানে তার প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই। কারণ তিনি বাঙালি।
উনিশ শতকের কথা। তখনো আমরা ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
দারোয়ান এসে জগদীশচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করল, বাবু আর কতক্ষণ কাজ করবেন। অনেক রাত হলো যে! গাড়ি-ঘোড়া তো কিছুই পাবেন না। বাড়ি যাবেন কীভাবে?
জগদীশচন্দ্র তার পকেট ঘড়িটি বের করলেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। দুপুরে ক্লাস শেষ করে সেই যে এসে ঢুকেছেন কখন যে এত সময় গড়িয়ে গেছে খেয়ালও করেন নি। এতক্ষণে টের পেলেন খিদে পেয়েছে। কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে ছিলেন খাবারের কথাও ভুলে গিয়েছিলেন।
আজ আর না। এখন বাড়ি ফেরা দরকার। অবলা নিশ্চয়ই না খেয়ে অপেক্ষা করছে।
বাড়ি ফেরাও ঝামেলার। দূরের পথ। শহর থেকে দূরে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। নির্দিষ্ট কোনো উপার্জন নেই তার।
থাকবেই বা কীভাবে? কলেজ থেকে তিনি তো কোনো বেতনই নেন না। পত্রিকায় কলাম লিখে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন।
বেতন না নেয়ার একটি কারণ আছে। আত্ম সম্মানবোধ। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জগদীশ বসু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন, ব্রিটিশ শিক্ষকদের চেয়ে অর্ধেকেরও কম বেতন দেয়া হলো তাকে। তিনি তা নিতে রাজি হন নি। বলেছিলেন, ‘যেদিন আমি ন্যায্য বেতন পাব সেদিনই নেব, তার আগে নয়।’
কোনো বেতন-ভাতা ছাড়াই তিনি অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন। দায়িত্বে আন্তরিকতার কোনো কমতি নেই। ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাস নেয়া। তাদের বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। আবার নিজ গবেষণাও করছেন পুরোদমে।
গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই ডিজাইন করছেন। বানিয়ে নিচ্ছেন স্থানীয় মিস্ত্রিদের দিয়ে। তার কথা হলো, ‘আমাদের যন্ত্র আমাদেরই বানানো শিখতে হবে।’ এসব খরচও নিজেকেই বহন করতে হচ্ছে তার। তবুও বেতন বা অধিকার আদায়ের জন্যে কারো শরণাপন্ন হন নি। জড়ান নি কোনো বিতর্কে।
তিন বছর এভাবেই চলল। এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ আর পারল না। তারা পরাজিত হলো জগদীশের অহিংস নীতির কাছে। বাধ্য হলো তাকে পূর্ণ মর্যাদায় ব্রিটিশ শিক্ষকদের সমকক্ষ বেতন দিতে। উপরন্তু তিন বছরের বকেয়া বেতনও পরিশোধ করল।
সাহস জুগিয়েছেন সহধর্মিণী অবলা বসু
তিন বছরের অর্থ একসাথে পেয়ে জগদীশচন্দ্র কলকাতা শহরে একটি বাসা ভাড়া নিলেন। বড় বারান্দা। পরিসরও বেশ। নতুন বাসায় অবলা কিছুটা স্বস্তি পেলেন। বিয়ের পর থেকেই তো সংসারে দেখছেন অর্থকষ্ট। যদিও তিনি বড় হয়েছেন কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তবে স্বামীকে কখনো বুঝতে দেন নি। পাশে ছিলেন সবসময়।
জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসুর মতো মেধাবী বাঙালি নারী সে যুগে কমই ছিল। ১৮৮১ সালে প্রবেশিকা পাশ করে তিনি মেডিকেলে পড়ার জন্যে আবেদন করেন। কিন্তু নারী হওয়ার কারণে কলকাতার মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করে দেয়। এটি তার খুব আত্মসম্মানে লাগে। যেভাবেই হোক তিনি মেডিকেলে পড়বেনই। কি আর করা! তার বাবা দুর্গামোহন দাস তাকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিলেন মেডিকেলে পড়তে। তিন বছর পড়াশোনাও করলেন। জগদীশের সাথে তার বিয়ে হলো ১৮৮৭ সালে। স্বামীর সংসারে এলেন। এরপর মেডিকেলে পড়া আর হয়ে ওঠে নি।
জগদীশচন্দ্র ও অবলার কোনো সন্তান ছিল না। তাই বলে ৫০ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাদের সুখের কোনো অভাব হয় নি। দুজনের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক ছিল। সুযোগ পেলেই তারা ভ্রমণে যেতেন।
একবার জগদীশচন্দ্র অকপটেই বলেছেন, ‘আমার স্ত্রীরত্নের সহযোগিতা না পেলে বিজ্ঞানের সাধনায় সফল হওয়া কঠিনই হতো। সম্ভবত আমার কোনো প্রচেষ্টাই আলোর মুখ দেখত না। মাঝপথে তা উল্টে পড়ত মুখ থুবড়ে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে আমি অবলার কাছে চিরঋণী।’
সভ্যতাকে উপহার দিলেন নতুন এক বিজ্ঞান
গবেষণা করতে করতে একদিন হঠাৎ তিনি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সাথে মিল খুঁজে পেলেন আলোক তরঙ্গের। অবাক হলেন। আরো মনোনিবেশ করলেন। দেখলেন আসলেই তো তা-ই। তারবিহীন যে প্রযুক্তি আবিষ্কারের তিনি চেষ্টা করছিলেন, মনে হচ্ছে তা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। তার আনন্দের মাত্রা তখন এতই বেশি যে ঠিক করলেন- বিষয়টি খাতায় লিখে রাখা দরকার।
তড়িৎ চুম্বকীয় এই তরঙ্গের তিনি নাম দিলেন ‘অদৃশ্য আলোক’। লিখলেন, ‘অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে।’
এবার প্রমাণ কারার পালা। ১৮৯৫ সাল। কলকাতার টাউন হল লোকারণ্য। ৭৫ মিটার দূরত্বে তালাবদ্ধ একটি ঘরে সিগন্যাল পাঠিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার চেপে পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। অনেকে মনে করল এটি জাদু। জগদীশচন্দ্র একটু হাসলেন। আর সভ্যতা পেল তারবিহীন নতুন এক প্রযুক্তি।
এবছরই তিনি মাত্র পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আদান-প্রদানের একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করলেন। পাশ্চাত্যের বড় বড় বিজ্ঞানীরা তখনো এত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। জগদীশ বসু তার এই আবিষ্কারের পেটেন্ট করলেন না। বরং সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন।
পরের বছর ইতালীয় বিজ্ঞানী জি. মার্কনি ২৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রেরণ করে দেখালেন। সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে পড়ল, মার্কনি হলেন বেতার বিজ্ঞানের আবিষ্কারক। ১৯০৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারও পেয়ে গেলেন তিনি।
জগদীশ বসুর নাম কেউ নিলেন না। পরাধীন একটি দেশের নাগরিককে কে মূল্যায়ন করবে? চাপা পড়ে গেল তার কৃতিত্ব।
এতে জগদীশ বসুর কিছুই যায়-আসে না। তিনি থেমে থাকেন নি। কখনো চান নি কোনো স্বীকৃতি। বরং এগিয়ে নিয়েছেন তার গবেষণা। বর্তমানে সত্যটি কিন্তু সবাই জানে। জগদীশচন্দ্র নাকি মার্কনি, রেডিও বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা কে?
পরবর্তীতে জগদীশচন্দ্রের তারবিহীন এ প্রযুক্তি রেডিও ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে টেলিভিশন, রাডার ইত্যাদি সিগন্যাল প্রেরণে। এমনকি আধুনিক ওয়াইফাই প্রযুক্তির উদ্ভাবনেও তার দেয়া তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
যুগের চেয়ে এক শতাব্দী এগিয়ে ছিল তার প্রযুক্তিজ্ঞান
বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। আইনস্টাইন জগদীশের বিভিন্ন আবিষ্কার সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন। একবার বলেছিলেন, ‘জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির জন্যে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।’
তার আবিষ্কারের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র ছিল না। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সলিড স্টেট ফিজিক্সে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আবিষ্কার করেন সেমিকন্ডাক্টর রেক্টিফায়ার।
পদার্থবিজ্ঞানে তিনি যেমন অবদান রেখেছন তেমনি জীববিদ্যায়ও সিদ্ধহস্ত। জীব ও জড়ের মধ্যে যে মেলবন্ধন তিনি লক্ষ করেছিলেন তখনকার সময়ে এভাবে কেউ ভাবতেই পারে নি। তার গবেষণা সেকালের তুলনায় এতটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল যে, বেতার বিজ্ঞানের ছড়ানো ছিটানো গবেষণাগুলো সুসংহত করার জন্যে ১৯১৯ সালে যখন ইন্টারন্যাশনাল রেডিও সায়েন্স ইউনিয়ন গঠিত হয়, দেখা যায় এর আটটি শাখার ছয়টির সাথেই জগদীশের কাজের সম্পর্ক! এমনকি ১৯৯০ সালে বায়োইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ে একটি নতুন কমিশন গঠনের পরও বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণাতেও জগদীশই ছিলেন পথিকৃৎ! তিনি তার যুগের চেয়ে শতাব্দীকাল এগিয়ে ছিলেন।
গাছেরও প্রাণ আছে, আছে অনুভূতি!
গাছের যে প্রাণ আছে—একথা তিনিই প্রথম বলেন। আরো বলেন, এটি কোনো জড় পদার্থ নয়।
বিদ্যুৎ ও আলো নিয়ে গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গাছ নিয়েও গবেষণা করেছেন প্রায় ৩৩ বছর। নিরলস গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন শতাধিক যন্ত্র। এসব যন্ত্র দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গাছের জীবনচক্র এবং গাছের অনুভূতির নানা রহস্য। গাছও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। ভয় পেলে কীভাবে কুকড়ে যায়। আবিষ্কার করলেন কম্পাউন্ড লিভার ক্রেস্কোগ্রাফ। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন গাছের বৃদ্ধি কখনো দ্রুতলয়ে, কখনো ধীরগতিতে বিরতিসহ।
তার গবেষণা ও উপলব্ধির কথা বর্ণনা করেছেন ‘গাছের কথা’ লেখাটিতে। খানিকটা এখানে তুলে ধরা হলো, ‘গাছের জীবন মানুষের ছায়ামাত্র। তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল দেখিয়াছ। মনে কর কোনো গাছের তলায় বসিয়াছ। গাছের নিচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। একসময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উঁই ধরিয়াছে। কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা বলত—এই গাছ আর মরা ডালে কী প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একটিতে জীবন আছে আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবন তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?’
‘রিক্ত হাতে এসেছিলাম, রিক্ত হাতেই ফিরে যাব’
তিনি ভালোমতোই বুঝতে পেরেছিলেন, গবেষণাগার ছাড়া নতুন কিছু উদ্ভাবন সম্ভব নয়। তখনো এই উপমহাদেশে বিজ্ঞান পাঠ তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিই প্রথম এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের চর্চা শুরু করলেন।
১৯১৭ সালে তার ৫৯ তম জন্মদিনে কলকাতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন গবেষণাগার ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’। সন্ধ্যা ছয়টায় উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘আজ যা প্রতিষ্ঠা করলাম তা মন্দির—কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নয়। সাধারণের সাধুবাদ শোনা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হয়ে অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে উদ্যত হয়েছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাদেরই জন্য।
বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই। সূক্ষ্ম নির্মাণও এদেশে কোনোদিন হতে পারে না, তা-ও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হলো, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারিয়েছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।
আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণাগারের জন্যে সর্বস্ব দান করছি। রিক্ত হাতে এসেছিলাম, রিক্ত হাতেই ফিরে যাব।’
মৃত্যুর আগেই তার উপার্জনের ১৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ১৩ লক্ষ টাকাই দান করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির ফান্ডে। তার মৃত্যুর পর অবলা বসুও বাকি সম্পত্তি দান করে দেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।
বর্তমানে বিখ্যাত এই গবেষণাগারটি ‘বোস ইনস্টিটিউট’ নামেই পরিচিত। প্রথম ২০ বছর এর প্রধান দায়িত্ব জাগদীশচন্দ্র নিজেই পালন করেছেন।
বাংলা ভাষার প্রথম সায়েন্স ফিকশন
তার-ব্যাটারি, বিদ্যুৎ আর উদ্ভিদ নিয়েই কি তিনি শুধু জীবন কাটিয়েছেন? কিন্তু না। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রেসপন্সেস ইন দ্য লিভিং এন্ড নন-লিভিং (১৯০২), প্ল্যান্ট রেসপন্সেস এজ এ মিনস অব ফিজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস (১৯০৬), কম্পারেটিভ ইলেক্ট্রফিজিওলজি (১৯০৭), নার্ভাস মেকানিজম অব প্ল্যান্টস (১৯২৫), কালেক্টেট ফিজিক্যাল পেপার্স (১৯২৭), মটর মেকানিজম অব প্ল্যান্টস (১৯২৮) ও গ্রোথ এন্ড ট্রপিক মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস (১৯২৯)।
ছোটদের জন্যে লিখেছেন 'অব্যক্ত'। এখানে রয়েছে বিজ্ঞানবিষয়ক ১০টি নিবন্ধ।
বাংলা ভাষায় প্রথম সায়েন্স ফিকশনও লেখেন তিনি ১৮৯৬ সালে। বইয়ের নাম ‘পলাতক তুফান’। তেল ঢেলে সমুদ্রের সাইক্লোন প্রতিহতের ঘটনা আছে এ বইটিতে।
দুই বন্ধু : একজন কবি অন্যজন বিজ্ঞানী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তার পরম বন্ধু। তাদের দুজনেরই প্রায় পত্রালাপ হতো। সাক্ষাৎ হতো। সুযোগ পেলেই বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন তারা। একবার রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘আমার জীবনের প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন, যেমন করে শরতে শিশির স্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই ঐশ্বর্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষের যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মাঝে আলো দেখেছিলুম।’
তার বাবা-মায়ের শিক্ষা ছিল দেশপ্রেম
জগদীশচন্দ্রের জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ময়মনসিংহে। পিতৃভূমি ছিল মুন্সিগঞ্জ। বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সন্তানকে তিনি শিশুকালে ইংরেজি মাধ্যমে না পড়িয়ে বাংলায় পড়িয়েছেন।
মা বামাসুন্দরী বসু স্বধর্মপরায়ণ নারী ছিলেন ঠিকই। কিন্তু জগদীশকে তিনি উদারনৈতিক একটি পরিবেশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। জগদীশকে ভিন্ন ধর্মের বন্ধুদের সাথে মিশতে দিতেন। প্রায়ই তাদের একসাথে বসিয়ে খাওয়াতেন।
জগদীশচন্দ্র তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন, ‘জীবনের এই প্রান্তে এসে আজ আমি বুঝে ফেলেছি, জীবনের সবচেয়ে টলটলে কাঁচা বয়সে কেন আমাকে বাংলা স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। নিজের ভাষা শেখো, নিজের ভাবে উদ্বুদ্ধ হও, নিজের ভাষার সাহিত্যের, স্বদেশের সংস্কার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হও। চিনে নাও নিজের উত্তরাধিকার। হৃদয়ঙ্গম করো, তুমি ওদেরই একজন। বিচ্ছিন্ন নও, শ্রেষ্ঠ নও।’
লন্ডনের কেমব্রিজে পড়াশোনা করতে গেলেও পড়া শেষ করে তিনি দেশে চলে আসেন। পরবর্তীতে গবেষক হিসেবে অনেকবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও তা নাকচ করেছেন অবলীলায়।
বিজ্ঞান ছিল তার সাধনা
অনেকেই তার আবিষ্কারগুলোকে পেটেন্ট করতে বলেছিলেন। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠিতে বলেন যে, ‘আমি যদি একবার টাকার মোহে পড়ে যাই তাহলে আর কোনোদিন এখান বের হতে পারব না। আমার আর আবিষ্কারের বিষয় থাকবে না। তখন থাকবে শুধু টাকা উপার্জন।’
আসলেই একজন জ্ঞান অনুসন্ধানী যখন অর্থ ও খ্যাতির মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তখন তিনি যুগ সৃষ্টি করেন। যা জগদীশচন্দ্র বসু তার কর্ম-সাধনায় প্রমাণ করেছেন। আর সভ্যতা হলো তার কাছে চিরঋণী। সত্যের জন্যে যখন কেউ কাজ করেন, তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি না পেলেও ইতিহাস তাকে মাথা নুইয়ে স্বীকৃতি দেয়। যেমনটা ঘটেছে মহান এই বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে।