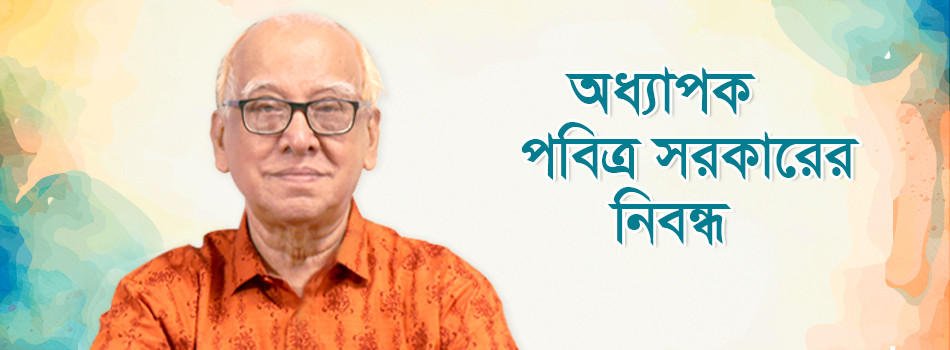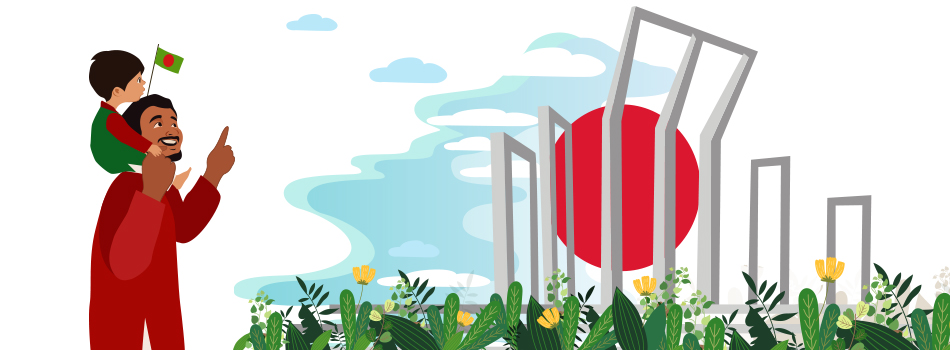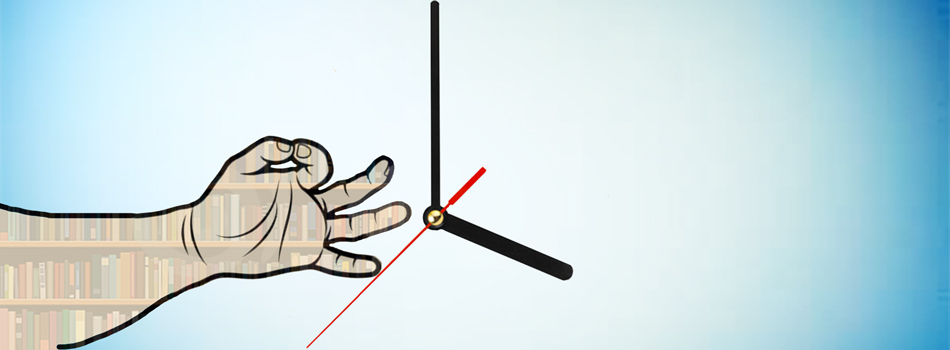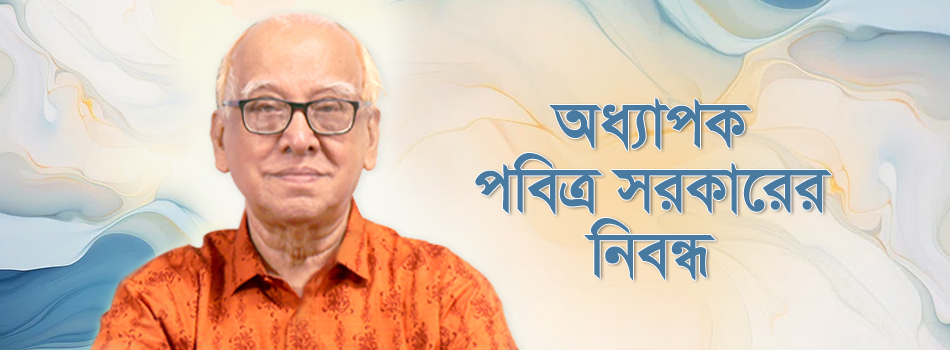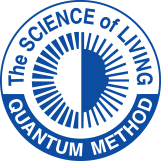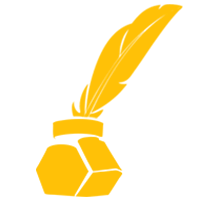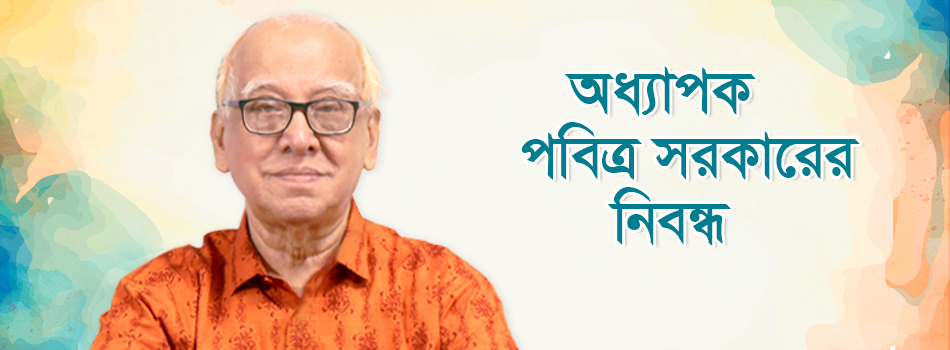
ভাষার জীবনমরণ
published : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩
শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, লেখক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার।
প্রাথমিক কথাবার্তা : ভাষার ক্ষয়, ভাষার মৃত্যু
দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা ভাষার মৃত্যু কথাটাকে কিছুটা আংশিক ও খণ্ডিতভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। ‘ভাষার মৃত্যু’ বলতে বুঝতাম পুরো গোষ্ঠী নয়, কিন্তু গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার কিছু লোক নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিচ্ছে, সন্তানদের সে ভাষা শেখাচ্ছে না—তাকে ব্যক্তিগত বা পরিবারগতভাবে ভাষার ‘ক্ষয়’ বা loss বলে দেখা হতো। অর্থাৎ কিছু লোক অন্য ভাষার লোকেদের মধ্যে গিয়ে পড়ায় (চাকরি সূত্রে, অভিবাসনের জন্য, উদ্বাস্তু হয়ে ইত্যাদি কারণে) তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না, তার ফলে আস্তে আস্তে নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিচ্ছে, নতুন জায়গার ভাষা তুলে নিচ্ছে তারা এবং তাদের সন্ততিরা। যেমন অবস্থা হয় বিদেশে প্রবাসী বাঙালি ও তাদের সন্তানদের। বাবা-মায়েরা হয়তো নিজেদের ভাষা কষ্টেসৃষ্টে বজায় রাখে, কিন্তু সন্তানেরা সেখানে রেডিও শুনে টেলিভিশন দেখে, ওই ভাষার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে এবং স্কুলে পড়ে অন্য ভাষার সমুদ্রে এমনই ডুবে যায় যে, তাদের বাপ-মায়ের ভাষা তাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়। কখনো কখনো ভাষাটা তাদের মস্তিষ্কে অক্রিয় (passive) ভাবে বেঁচে থাকতেও পারে, অর্থাৎ অন্যে সে ভাষা বললে তারা তা বোঝে। কিন্তু তারা যদি বিদেশে বিদেশি বা বিদেশিনী বিয়ে করে, তা হলে তাদের সংসারে সন্তানেরা সাধারণভাবে সে ভাষা শিখবে না।
এই language loss বা ভাষাক্ষয়ের উল্টো প্রক্রিয়া হলো ভাষারক্ষণ বা language maintenance। অর্থাৎ ভাষাটি ভাষীরা হারাতে দিচ্ছে না, নানা ক্ষেত্রে রক্ষা করছে। সেটার জন্য যে লড়াইটা করা দরকার অনেকেই তা করার জন্য যথেষ্ট পারিপার্শ্বিক সমর্থন পায় না (চারপাশে নিজের ভাষা বলার মতো যথেষ্ট লোক নেই), কিংবা নিজেরা যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করে না (‘ও ছাই ভাষা রেখে আর কী হবে, এদেশে এই ভাষাতেই যখন থাকব’?), তখন তারা নিজেদের ভাষা হারাতে থাকে। এই ভাষারক্ষণ আর ভাষাক্ষয়—এই দুই প্রবণতার মধ্যে ভাষারক্ষণ কিছুটা স্রোতের উজানে নৌকা বাওয়ার মতো, প্রতিবেশের চাপের ফলে ভাষাক্ষয়ের শক্তিই যেন বেশি। এ দুয়ের মধ্যে দড়ি-টানাটানিতে অধিকাংশে ক্ষেত্রে ক্ষয়ের শক্তিই জিতে যায়।
যখন এই দুটি বিপরীতমুখী এবং দ্বান্দ্বিক প্রবণতাকে লক্ষ করা হতো, তখন সমগ্র ভাষাগোষ্ঠী বিবেচনার বাইরে থাকত। দেখা হতো মূল ভাষাগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পরিবার বা গোষ্ঠীকে—যারা ভাষাভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র অন্য ভাষাভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলেই ধরে নেওয়া হতো—এমন একটা সাংস্কৃতিক ঘটনা যা স্বাভাবিক এবং খুব মারাত্মকভাবে নেতিবাচক নয়। মাইশোরের কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থান বা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস থেকে এ ধরনের অনেক পুস্তিকা আগে বেরিয়েছিল, যাতে ব্যাঙ্গালোরে বাঙালি ছেলেমেয়ের ভাষা, বা দিল্লিতে কন্নড় ছেলেমেয়ের ভাষার রক্ষণ ও ক্ষয়ের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা ছোট একটি সমষ্টির ভাষার এই ক্ষয়কে ‘ভাষার মৃত্যু’ হিসেবে গণ্য করা হতো না, কারণ মূল ভাষাভূমিতে ভাষাটা তো অন্তত অক্ষত আছে—এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তগুলি তার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না—এমনই মনে করা হতো। হয়তো এখনো হয়।
‘ভাষার মৃত্যু’ হলো নিজের ভাষাভূমিতে, নিজের হাজার বছরের ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রতিবেশে লালিত ও পুষ্ট ভাষাটির মৃত্যু অর্থাৎ বিলয়। আগেরটা যদি loss হয়, এটা সম্পূর্ণত death। এর দ্বিতীয় একটি শব্দ shift, তা আমরা পরে দেখব, কিন্তু আমাদের কাছে ‘মৃত্যু’ কথাটাই বেশি আবেদন তৈরি করে। তবে ভাষা নিজে তো মরে না, আসলে এক দিক থেকে ‘মরে’ ভাষার বক্তারা। এমনকি যদি মাত্র একজন বক্তাও বেঁচে থাকে তা হলেও ভাষাটা মরে গেছে ধরতে হবে, কারণ যে বেঁচে আছে, তার নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য আরেকটা লোক নেই। অন্তত দুজন লোক না থাকলে ভাষা বেঁচে আছে বলা যাবে না। এইরকম জানা গেছে ইংল্যান্ডের কর্নিশ ভাষার শেষ বক্তা মাউস্হোলের শ্রীমতী ডলি পেন্ট্রিথ বেঁচে ছিলেন ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ২০১০-এর ৪ ফেব্রুয়ারি খবর বেরোল, ভারতের আন্দামানের বো ভাষার শেষ বক্ত্রী আর বেঁচে নেই। এইভাবে মরে গেছে আইল অব ম্যান-এর ম্যাংক্স (Manx) ভাষা।
ক্রিস্টাল (Crystal, 2000 :50) একটি পরিসংখ্যান তুলেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামার স্কুল অব লিঙ্গুইস্টিক্স-এর মুখপত্র Ethnologue-এর ১৯৯৯-এর একটি সমীক্ষা থেকে—পৃথিবীতে ৫১টি ভাষায় একজন মাত্র বক্তা বেঁচে আছে, ৫০০ ভাষায় বক্তা ১০০-র কম, ১৫০০ ভাষায় ১০০০-এর বেশি নয়, ৩০০০ ভাষায় ১০০০০-এর মতো বক্তা, আর ৫০০০ ভাষায় বক্তা এক লক্ষের কাছাকাছি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যাদের ভাষা এক লক্ষ লোক বলে তাদের ভাষার বিপদ এমন কী বেশি? এর উত্তরে পৃথিবীর বৃহৎ ভাষাগুলির বক্তাসংখ্যা উদ্ধার করা যেতে পারে—ইংরেজির বক্তারা সব মরে যায়—তার ফলে পুরো ভাষাটা মরে যায়—এ কথাটাও কেবল একটি অর্থে সত্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তারা দিব্যি বেঁচে থাকে, কিন্তু তারা নিজেদের এতদিনকার নিজস্ব ভাষাটা বলা (বা লিখিত ভাষা হলে লেখা) ছেড়ে দেয়। বলা উচিত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ প্রতিবেশের রাজনীতি-শিক্ষানীতি-অর্থনীতি তাদের বাধ্য করে ভাষাটা ছেড়ে দিতে। নিজেদের ভাষা ছেড়ে তারা অন্যদের ভাষা বলতে শুরু করে। একে বলে ‘ভাষালম্ফন’, ইংরেজিতে কারো কারো কথায় language shift। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষার মৃত্যু ঘটে ওই ভাষালম্ফন বা আরো স্পষ্ট কথায় ভাষাবর্জনের ফলে। এই ভাষাবর্জন সচেতন, বক্তারা জেনেশুনে একভাষা ছেড়ে অন্য ভাষা ধরে, মাঝখানে হয়তো একটা দ্বিভাষিকতার স্তর পার হয়ে যায়। দুটো ভাষাই তখন পাশাপাশি বলে, তার পর আস্তে আস্তে নিজের ভাষায় অন্য ভাষার উপাদান বেশি ঢুকে পড়ে, তার পর অন্য ভাষাটাই তার জিহ্বাকে পুরোপুরি দখল করে নেয়। অনেক অভিবাসী পরিবার বিদেশে গিয়ে যে নিজেদের ভাষা ছেড়ে দেয় সেটা এই রকম। নিজের ভাষার প্রতি অবহেলা (হয়তো প্রতিবেশের চাপে), অবহেলা থেকে মাতৃভাষার ক্ষয়, ক্ষয় থেকে শেষে মৃত্যু। এই জন্য অনেকে ‘ভাষার মৃত্যু’ ‘ভাষার হত্যা’—এই ধরনের কড়া কথার বদলে ভাষালম্ফন বা language shift কথাটাই বেশি পছন্দ করেন। এটা অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। ভাষার মধ্যে থেকে যে দেখছে, যার মাতৃভাষা হারিয়ে গেল, সে তো ভাবতেই পারে আমার মাতৃভাষাকে খুন করা হলো। আর নিরাসক্ত বিজ্ঞ যিনি বাইরে থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করেন, তিনি দেখেন লোকেরা নিজেদের ভাষা ছেড়েছে বটে, কিন্তু ভাষা তো একটা বলছে তারা। কাজেই ভাষার লম্ফন ঘটেছে, মৃত্যু নয়।
আমরা এটাকে, আগে যেমন বলেছি, মৃত্যুই ভাবি। কারণ ওই ভাষার নামটা তো আর ব্যবহার্য, সচল কিছু বোঝাচ্ছে না, তা তো ইতিহাসের বস্তু হয়ে যাচ্ছে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুর মৃত্যু ঘটছে—গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের, অর্জিত ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সংস্কৃতির।
ভাষার আরেক ধরনের মৃত্যু আছে, যেটা আক্ষরিক অর্থে মৃত্যু নয়, ফলে তা নিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান না। সেটা হলো বিবর্তনের ফলে মৃত্যু। ভাষা পরিবর্তিত হতে হতে একসময় এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছাল যখন আর তাকে সেই ভাষা বলে চেনা গেল না, তার মধ্য থেকে অন্য ভাষার জন্ম হয়েছে। এইভাবে ইউরোপে একদিন কথ্য লাতিন ভেঙে ফরাসি, স্প্যানিশ, পোর্তুগিজ, ইতালীয়, রুমানীয়—এই সব ভাষার জন্ম হয়েছিল, ভারতে সংস্কৃত (তার কথিত রূপ) থেকে প্রাকৃত ভাষাগুলির, আবার প্রাকৃত থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির। এক্ষেত্রে নতুন ভাষার জন্ম মানে পুরনো ভাষার মৃত্যু, নতুন ভাষা প্রায় মাতৃঘাতী সন্তানের মতো। কিন্তু এ হলো ভাষার বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, মানবজীবনের রূপক অনুসরণে বলা যায়, নতুন ভাষার জন্ম পুরনো ভাষার মৃত্যুকে সহনীয় করে। এ থেকেই ভাষার সঙ্গে নদীর উপমা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এই নিবন্ধে ভাষার যে মৃত্যুর কথা বলছি তা হলো ভাষার বংশলোপ। নদীর মরুভূমিতে এসে স্রোত হারিয়ে ফেলার মতো। প্রাচীনকালে পশ্চিম এশিয়ায় তোখারীয় ভাষার মৃত্যু এইভাবে ঘটেছিল।
ভাষার যে মৃত্যু নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিকর্মীরা চিন্তিত তা হলো যাকে শ্রীমতী স্কুৎনাব্-কাঙ্গাস (2000 : xxxi-xxxiii) বলেন linguistic genocide’ বা language murder—এই তীব্র শব্দ দুটি সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি আছে জেনেও। যেখানে একটি ভাষা নিজের ভূমিতে থেকে, অন্য ভাষার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষাগত চাপে নিজের বক্তাদের হারিয়ে ফেলতে থাকে। এথনোলগ্ পত্রিকাটির (এটি মাঝে মাঝে পৃথিবীর ভাষার গোটা হিসেব জানায়) ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে ওই সময়ে ৬৯১২টি ভাষা বলা হচ্ছিল। তার মধ্যে ইউরোপের ভাষা ২৩৯টি, আফ্রিকার মোট ২০৯২টি। এথনোলগ কাকে ভাষা বলেছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও এই ভাষাগুলির বাঁচনমরণ বিষয়ে দুটি কথা সকলেই স্বীকার করে নেন : প্রথমত, প্রথম যখন মানুষের ভাষা শুরু হয় তখন ভাষার সংখ্যা প্রায় এর দ্বিগুণ ছিল—অর্থাৎ প্রায় ৩০-৪০ হাজার বছরের মধ্যে মানুষের অর্ধেক ভাষা লুপ্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, আগামী ৭-৮ দশকে যা আছে তারও অর্ধেক সংখ্যক ভাষা লুপ্ত হবে।
যা লুপ্ত হবে সেগুলি সবই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা। এই গোষ্ঠীগুলি কেবল জনসংখ্যায় ক্ষুদ্র নয়, তারা এবং তাদের ভাষা ক্ষমতার দিক থেকেও দুর্বল। পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল ভাষাগুলির সংখ্যাই বেশি, মোট ভাষার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ লোক এই প্রায় ৪ হাজারের মতো ক্ষুদ্র ভাষা বলে। এরা অধিকাংশতই প্রযুক্তিহীন অনাগরিক জীবনের অধিবাসী, কেউ কেউ অরণ্যচারী এবং যেমন বলা হয়েছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে খুবই পশ্চাৎপদ। ফলে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী এবং তাদের ভাষার চাপ এদের ভাষা সহ্য করতে পারে না, এদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও দুর্বল।
কয়েকটি আখ্যান
ইয়ানসেনের (Jansen, 2012) বিবরণ থেকে আমরা কয়েকটি ভাষার মৃত্যু ও সংকটের ইতিহাস একটু বলি। আগে কর্নিশ ভাষার কথা বলেছি। এখন বলি স্কটিশ গেলিক (Gaelic) ভাষার কথা, যা মৃত্যুর দিকে চলেছে, প্রাণটা ধুকধুক করছে বলা যায়।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে স্কটল্যান্ডের পূর্ব সাদারল্যান্ড এলাকায় জনৈকা লেডি সাদারল্যান্ড ছিলেন বেশিরভাগ জমির মালিক। তিনি খাস ইংরেজ মহিলা। তার অধীনে থাকা গেলিকভাষী প্রজারা কোনোরকমে চাষবাস করে দিন চালাত, তাকে ফসলের অংশ বা খাজনা দিত। কিন্তু দেশ আর বিদেশের বাজারে ভেড়ার মাংস আর পশমের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। তাই জমিদারনি ঠিক করলেন চাষবাসের চেয়ে ওই মাংসের ব্যবসাতে লাভ অনেক বেশি, তাই চাষ আর করবেন না, জমিগুলো ভেড়া চরাতে ব্যবহার করবেন। কৃষির বদলে পশুপালন।
চাষিরা ওই অঞ্চল থেকে উৎখাত হলো। তাদের জীবিকা আর বাসস্থান কেড়ে নেওয়ার আরেকটি কারণও নাকি ছিল। ইয়ানসন মহিলার ম্যানেজার প্যাট্রিক সেলার্সের কথা উদ্ধার করেছেন—‘their obstinate adherence to the barbarous jargon of the times when Europe was possessed by Savages.’ অর্থাৎ তারা ইংরেজি বলত না, বলত ‘প্রাচীন ইউরোপের বর্বর জনগোষ্ঠীর একটি ভাষা’। ফলে শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনা নয়, একটি প্রবল ভাষাবিদ্বেষও কার্যকর ছিল। ম্যানেজার মশাইয়ের জানার কথা নয় যে ওই ভাষা কেল্টিক গোত্রের, তার সঙ্গে লাতিন গোত্রের ভাষাগুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে—যে লাতিন কি না দীর্ঘদিন ইংরেজদের ধর্মের ‘পবিত্র’ ভাষা ছিল। কিন্তু যেমন হয়, চারপাশের তথাকথিত ‘উন্নত’ ভাষার মানুষের অবজ্ঞা, ধিক্কার ও বিদ্বেষ কোনো ভাষার মানুষদের মনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে একটা ভাষাহীনম্মন্যতার বোধ জন্মাতেই পারে, সে ভাবতেই পারে যে, আমার ভাষাটা ওদের উপহাসের বস্তু, এটা বলতে আমার লজ্জা হয়, কাজেই ‘ও ভাষা, তুমি যাও!’
যাই হোক, শ্রীমতী সাদারল্যান্ডের চাষীদের বলা হলো, বাপু হে, তোমরা চাষের জমি ছেড়ে ভাগো, সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছটাছ ধরে দিন চালাও। চাষীদের শূন্য জায়গা পূরণ হলো দক্ষিণের সমতলভূমির ইংরেজিভাষী পশুচারকদের দিয়ে। চাষীরা সমুদ্রের ধারে মাছ ধরে কোনোরকমে টিকে রইল বটে, কিন্তু তারা আগের তুলনায় গরিব হয়ে গেল।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের গ্রামেও ইংরেজি ভাষার দাপট শুরু হলো। গির্জায় ইংরেজি ব্যবহার হচ্ছে (ধর্মের ভাষার দারুণ শক্তি!), সরকার যে-সব ইস্কুল বসাচ্ছে সেখানে ইংরেজি একমাত্র ভাষা। চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ—সবকিছুর বাহন ইংরেজি। গ্রামেও ইংরেজিভাষীরা এসে বাস করতে লাগল। তাদের উপস্থিতিতে গেলিকভাষীরাও গেলিক বলতে সংকোচ বোধ করত। যদি বাপ-মায়ের একজন কেউ ইংরেজি বলত তা হলে শিশু ইংরেজিভাষী হিসেবেই বড়ো হতো।
ফলে দু-তিন প্রজন্মের মধ্যেই গেলিকভাষীর সংখ্যা সাংঘাতিক কমে এসেছে, যারা তা ধরে রেখেছে তারাও এখন খুবই বৃদ্ধ। আড়াইশো বছরের মধ্যেই একটি প্রবলভাবে জীবন্ত ভাষা মৃত্যুর কিনারায় এসে পৌঁছেছে। এই ঘটনা নিয়ে Language Death নামে বই লিখেছেন গবেষিকা ন্যান্সি ডোরিয়ান, সেই নামটি সম্বন্ধেই আপত্তি তুলে ইয়ানসন বলেছেন, তা কেন, তারা তো আরেকটা ভাষা বলছে। নাম হওয়া উচিত language shift। আমরা যারা অন্য ভাষার চাপ পদে পদে টের পাই, এ সম্বন্ধে আমাদের মত ভিন্ন, আমাদের মন্তব্য আমরা আগেই পেশ করেছি।
পৃথিবীর নানা জায়গায় ক্ষুদ্র ভাষার মানুষেরা সব শক্তিশালী ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কখনো ইংরেজি, কখনো স্প্যানিশ, কখনো পোর্তুগিজ। সাইবেরিয়ার বিশাল অঞ্চলে তাদের নিজেদের ভাষা অবলুপ্ত, রুশ ভাষার আধিপত্য। জার্মানির অস্ট্রিয়া অঞ্চলে হাঙ্গেরীয় ভাষা অবলুপ্ত হয়ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে পাপুয়া নিউ গিনিতে কয়েকশো ভাষার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘টোক্ পিসিন’ নামে এক মিশ্রভাষা, তা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রথম ভাষা হতে চলেছে। উত্তর আমেরিকায় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রায় ইউরোপীয়রা পৌঁছোবার সময়ে তিনশো আদি আমেরিকান ভাষা বলা হতো। ১৯৬০ নাগাদও প্রায় দুশো ভাষার অস্তিত্ব ছিল। গত কয়েক দশকে তার সংখ্যা বিপুলভাবে কমে এসেছে। অস্ট্রেলিয়াতে দিরবাল (Dyirbal), মেক্সিকোতে নাহুয়াত্ল্ (Nahuatl) ভাষা মরণোন্মুখ। ইয়ানসনের মতে আফ্রিকাতে নিজের ভাষা ছেড়ে সকলে যে স্থানবিশেষে নিজের অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা ইংরেজি গ্রহণ করছে, সে ঘটনা তত প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো সমস্যা হলো নিজের ক্ষুদ্র ভাষা ছেড়ে অনেক গোষ্ঠী কাছের বৃহৎ ও শক্তিশালী আফ্রিকার ভাষাতেই আশ্রয় নিচ্ছে। তানজানিয়া আর কেনিয়াতে সে ভাষা সোয়াহিলি, জিম্বাবুয়েতে শোনা, নাইজিরিয়াতে হাউসা, ইয়োরুবা বা ইগবো-র মধ্যে যে-কোনো একটা। বোত্সোয়ানাতে আবার ক্ষুদ্রতর ভাষা (৫ থেকে ১০ হাজার) থিম্বুকুশু আকর্ষণ করছে বৃহত্তর ভাষা শিয়েয়ি-র বক্তাদের (২৫ হাজার), ফলে শিয়েয়ির ভাষীসংখায় দ্রুত কমছে, থিম্বুকুশুর বাড়ছে। তার প্রধান কারণ শিয়েয়ি যারা বলে তারা অপেক্ষাকৃত ছড়ানো-ছিটোনো, তাদের সামাজিক সংহতি কম, ঐতিহ্য সম্বন্ধে তারা কম সচেতনও বটে। সেদিক থেকে থিম্বুকুশু-ভাষীরা তাদের চেয়ে সংহত ও নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তারা তাদের ভাষা ছাড়তে আগ্রহী হয় নি।
ভারতে এখন ৭৮০টির মতো ভাষা বলা হয়, কিন্তু গত ৫০ বছরে ২২০টি ভাষা অবলুপ্ত হয়েছে। দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ভাষাগুলির মৃত্যু হয়েছে বেশি। বাংলাদেশে দ্রাবিড় গোত্রের মালপাহাড়িয়া, ভোট-বর্মি গোত্রের খুমি, ঠার/ঠেট, লালং ইত্যাদি ক্ষুদ্র ভাষা বিপন্ন পর্যায়ের (দ্র. সিকদার, ২০১২ : ২০৩-২২৪)। সিকিমে নামি মাঝি ভাষার ৪ জন বক্তা মাত্র টিকে আছে, ত্রিপুরার চইমাল ভাষার আছে ৪-৫ জন। ভাষাবিজ্ঞানীরা তো এই ভয়ই করছেন যে, পৃথিবীতে এখন যে ৬৯০০টির মতো ভাষা বলা হয় তার অর্ধেকই এই শতাব্দীতে শেষ হয়ে যাবে।
মৃত্যুর আগে ভাষার বিপন্নতার কয়েকটি পর্যায়ও লক্ষ করা হয়েছে। এক, প্রথমে ‘হবু বিপন্ন’ (Potentially Endangered)—যেখানে ভাষাটি একটি বড় ও প্রতাপান্বিত ভাষার সংস্পর্শে এসেছে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো ‘বিপন্ন’ (Endangered), যখন ছোটরা সে ভাষা কম শিখছে, আর কেবল যুবকদের এবং প্রবীণদের মধ্যেই সে ভাষার স্বচ্ছন্দ বক্তা পাওয়া যাচ্ছে। তিন হলো ‘রীতিমতো বিপন্ন’ (Seriously Endangered) যখন ৫০ বছরের কমবয়েসিদের মধ্যে সে ভাষার স্বচ্ছন্দ বক্তা বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। আর ভাষার ‘মৃতপ্রায়’ (Moribund) অবস্থা হলো যখন কিছু বৃদ্ধই বলতে পারে ও ভাষা, কমবয়েসিরা অন্য ভাষা বলে।
কেন ভাষার মৃত্যু ঘটে ?
অর্থাৎ কোনো গোষ্ঠী কেন নিজেদের ভাষা বলা ছেড়ে অন্য ভাষায় চলে যায়? সাসে (হান্স ইয়ুরগেন সাসে, Sasse) এর পেছনে তিনটি কারণ নির্ধারণ করেছেন। এই তিনটি ক্রমান্বয়ী—অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির সূত্রপাত ঘটায় এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয়টিকে সম্ভব করার ফলে ভাষাবর্জনের ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হলো বহির্ব্যবস্থা (ES = External Setting), দ্বিতীয়টি হলো ভাষাচার (SB = Speech Behaviour), এবং তৃতীয়টি হলো ভাষার শরীরে তার প্রভাব (Structural Consequence)। অর্থাৎ ভাষা ক্রমশ বদলাতে বদলাতে কী করে অন্য ভাষা হয়ে যায় তার প্রক্রিয়া।
এর মধ্যে প্রথমটা হলো সবচেয়ে শক্তিশালী, কারণ এটাই অন্য দুটি ঘটনার কারণ। বহির্ব্যবস্থা মানে হলো, এমন এক দ্বিভাষিক পরিবেশ, যেখানে যে ভাষাটি লোপ পাবে তার পাশে আরেকটি আরো শক্তিশালী ভাষা সেই ভাষার ভাষীরা বলতে বাধ্য হবে। অন্য কথায় বলা যায়, যে ভাষা আমরা নানা কারণে বলতে বা শিখতে বাধ্য হই সেটাই আমাদের ভাষার চেয়ে শক্তিশালী ভাষা।
এমন নয় যে, ব্যক্তিগতভাবে কোনো শক্তিশালী ভাষার লোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষা শেখে না। শেখে গবেষণার জন্য, সাহিত্যপাঠের জন্য, ওই ভাষার স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য, হাটে-বাজারে ব্যবসা বা অন্য কাজকর্মের জন্য—এরকম নানা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ভাষার শক্তি-দুর্বলতা ব্যক্তির হিসেবে নয়, গোষ্ঠীর হিসেবে।
গোষ্ঠীগতভাবে কোনো ভাষা অন্য ভাষার চেয়ে শক্তিশালী হয় কখন? যখন সে ভাষা হয় প্রশাসনের ভাষা, স্কুলে শিক্ষার ভাষা, পাঠ সাহিত্যের ভাষা, পাঠ্য ও দৃশ্য-শ্রাব্য সংবাদ মাধ্যমের ভাষা, সর্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যের আর অফিস-আদালতের ভাষা, কখনো-বা ধর্মের ভাষা। আর সব বাদ দিয়েও, যদি কোনো ভাষার রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকে আর আমার ভাষার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে আমি সে ভাষা শিখতে বাধ্য হবো।
আমরা আমাদের উপভাষাগুলির সঙ্গে তুলনা করে ব্যাপারটা একটু বুঝে নিতে পারি। বাংলার মান্য চলিতের সঙ্গে কাছাকাছি যে-সব উপভাষা, সেগুলি ক্রমশ একরকম হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। কেন? না, ছেলেমেয়েরা স্কুলে বলছে মান্য চলিত, টেলিভিশনে শুনছে মান্য চলিত, বইয়ে পড়ছে মান্য চলিত। যাতায়াতের সুব্যবস্থার ফলে মান্য চলিতের ভিত্তিভূমির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ছে। তাই বাড়িতে বাড়ির ভাষা বা উপভাষার ব্যবহার কমছে। এই সব ছেলেমেয়েরা যখন বড় হবে তখন চাকরি-বাকরি, শিক্ষা-সংক্রান্ত আর সাংস্কৃতিক কাজকর্মে এরাও মান্য চলিতই ব্যবহার করবে। হয়তো বিবাহ করবে মান্য চলিতভাষী কাউকে। নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে—শহরের ভাষা, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে মূলত মান্য চলিত। এদের সন্তানেরা আর ঘরের ভাষা বা উপভাষা বলবে না। এইভাবেই উপভাষা ছাড়ছে অনেক মানুষ—শুধু বাংলার নয়, প্রায় সমস্ত বৃহৎ ভাষার।
উপভাষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টা প্রায় আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে। তা নিয়ে সাধারণত ক্ষয়ক্ষতির উদ্বেগ বা অপরাধবোধ জাগে না, ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সমাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার আনুষঙ্গিক কৃত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু একটা গোটা ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভবত এ বিষয়ে আমরা আরেকটু সচেতন হই।
‘গোটা ভাষা’ বলতে আমরা কী বুঝি তা একটু পরিষ্কার করি। পৃথিবীর অনেক ভাষাই একাধিক উপভাষার সমষ্টি। স্থানীয় উপভাষা, শ্রেণিগত উপভাষা। এ সম্বন্ধে সরকার (২০০৩ : ১০-১৩)-এ আমরা একটু বিস্তারিত করে লিখেছি। তার উপর অনেক সময় গড়ে ওঠে একটি মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা। এই সব ভাষারূপ নিয়েই একটা গোটা ভাষা। আমাদের বাংলাও তাই একটা বাংলা নয়, অনেকগুলি, অনেক রকমের বাংলা।
এমন হতেই পারে যে, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে এত রূপ-বৈচিত্র্য থাকে না। কিন্তু ভাষার মৃত্যু হলে যে-কটা রূপ আছে, কমই হোক, বেশিই হোক—সবই মরবে।
নানা কারণে অন্য ভাষা আমরা শিখতে বাধ্য হলেও তার মানে অবশ্য সবসময় এই দাঁড়ায় না যে, আমি আমার ভাষা ত্যাগ করে সেই ভাষার কোলে গিয়ে আশ্রয় খুঁজব। সেটা নির্ভর করে আমার ভাষার শক্তির উপর, আর আমি আমার গোষ্ঠীর সঙ্গে এক ভাষাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি কি না, আমার গোষ্ঠীসংহতি আছে কি না, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর। এই ভাষাভূমিতে, ভাষার নিজের ভৌগোলিক পরিসরে, আমার ভাষারও যদি অল্পবিস্তর ওই ক্ষমতাগুলি থাকে, তা হলে আমি আমার জীবিকার সুযোগ-সুবিধের জন্য বা জ্ঞানের জন্য অন্য আরো ক্ষমতাশালী ভাষা শিখব, কিন্ত নিজের ভাষাটাকে সহজে ছাড়তে চাইব না। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির ক্ষেত্রে যেমন দেখি। আমরা চাকরি-বাকরি সবকিছুর জন্য ইংরেজি শিখছি, কিন্তু দলে দলে আমাদের মাতৃভাষা—মারাঠি, গুজরাতি, হিন্দি, তামিল, মলয়ালম, বাংলা ছেড়ে ইংরেজি ভাষায় স্থায়ী অভিবাসন নিচ্ছি না, কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও।
এই জন্যে ইউনেস্কোর বিপন্ন ভাষার তালিকায় ইংরেজি যদি ০ ক্রমাঙ্কে থাকে (অর্থাৎ ইংরেজি বিপন্ন ভাষা আদৌ নয়), বাংলা, মারাঠি ইত্যাদি আছে ১ ক্রমাঙ্কে—এদের বিপন্নতার মাত্রা এখনো খুব কম। কিন্তু ইংরেজির মতো একটি শক্তিশালী ভাষা ঔপনিবেশিকতা আর বিশ্বায়নের ফলে এসব ভাষাকে যে রীতিমতো প্রভাবিত করছে, তার প্রমাণ ব্যাপক বুলিমিশ্রণ ও বুলিলম্ফন—বাংলার ক্ষেত্রে যার কিছুটা নমুনার জন্য সরকার (২০১৩ : ১৮৪-২০৩) দেখা যেতে পারে। বাঙালি ও অন্যান্য উপমহাদেশীয় ভাষার মানুষেরা প্রায়ই ইংরেজির সঙ্গে তাদের ভাষার ‘খিচুড়ি’ (হিংলিশ, বাংলিশ, তামলিশ ইত্যাদি) নিয়ে উদ্বিগ্ন হন এই কারণেই, ঠাট্টা-তামাশা করার সঙ্গে সঙ্গে। আমেরিকার বাঙালি মা অফিস যাওয়ার আগে বন্ধুর হাতে ছেলের দায়িত্ব দিয়ে ছেলেকে বলছেন, ‘তুমি নটি হয়ো না বাপি। তোমার আন্টি তোমাকে ক্যারট দিয়ে রাইস মেখে দেবে, বি আ গুড বয় অ্যান্ড ইট, কেমন?’ এই হলো মাঝারি অবস্থা, speech behavior-এর পরিবর্তন। এর পর ছেলে ইংরেজি বলবে, ভাষার সাংগঠনিক রূপান্তর ঘটবে। ভাষা অন্য ভাষার কাছে সব জায়গা ছেড়ে দেবে। জায়গা ছেড়ে দেওয়া মানে যে-সব ক্ষেত্রে (domain-এ) নিজের ভাষার ব্যবহার হয়, সেই ক্ষেত্রগুলি থেকে নিজের ভাষা ক্রমশ পশ্চাদপসরণ করবে—শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আদান-প্রদান—সব জায়গায় শক্তিশালী ভাষাটি এসে জায়গা দখল করবে।
বড় ভাষাগুলিরই যদি এই দশা, তা হলে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে ছড়িয়ে থাকা ছোট ভাষাগুলির কী অবস্থা হতে পারে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য নয়। ইংরেজি, স্প্যানিশ, রুশ, আরবি ইত্যাদি অনেক ভাষাই বহু ছোট ভাষার অবলুপ্তির কারণ হয়েছে, ফলে এসব ভাষা killing language—এই অবাঞ্ছিত শিরোপা পেয়েছে।
ভাষার মৃত্যু কত রকমের—স্যাসের প্রবন্ধে তারও একটি শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। ভাষার আকস্মিক মৃত্যু (Sudden Death) ঘটে যখন একসাথে সব ভাষীকে যুদ্ধে বা কোনোভাবে মেরে ফেলা হয়, তাসমানীয় ভাষার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছিল। চাপানো মৃত্যু (Radical Death) ঘটে যখন শাসক বা শক্তিশালী ভাষার মানুষদের অত্যাচারে ভাষীরা আত্মরক্ষার জন্যেই নিজেদের ভাষা বলা বন্ধ করে। মার্কিনদেশে বহু আদি আমেরিকান ভাষার মৃত্যু এইভাবে ঘটেছে। সেখানকার একভাষী (‘শুধু ইংরেজি’) নীতিতে আদি আমেরিকান ছাত্রদের নিজেদের ভাষা বললে শাস্তি দেওয়া হতো, শুয়োরের কাটা মাথা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ক্রিস্টাল (2004 : 51) ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর তথ্যগুলি তুলে ধরেছেন। ইউরোপিয়ানরা আমেরিকায় যাওয়ার আগে আদি আমেরিকান (Native American)-দের সংখ্যা ছিল ১০ কোটির মতো। ১৫১৮-তে তাদের সংখায় কমে দাঁড়াল আড়াই কোটি; আর ১৬২০-তে সে সংখ্যা নেমে এলো ১ কোটি ৬০ লক্ষে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসায় এইভাবে বহু জনগোষ্ঠী আর তাদের ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে।
আর ক্রমবদ্ধ মৃত্যু (Gradual Death) ঘটে যখন ধীরে ধীরে ভাষাটি বিলুপ্ত হয়, যা পৃথিবীর অধিকাংশ লুপ্ত ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আর শেষটি হলো ‘তলা-থেকে-উপরে মৃত্যু’ (Bottom-to-Top Death)। তাতে ভাষাটি ধর্মাচরণ বা আচার-অনুষ্ঠানের ভাষা হয়ে থাকে, মানুষের মুখে আর বেঁচে থাকে না। মিশরে কপটিক ভাষা এমন হয়েছিল, বিবর্তনের ফলেও এমন ঘটতে পারে, যেমন ঘটেছে আমাদের সংস্কৃতের ক্ষেত্রে।
ভাষার পুনরুজ্জীবন
যে ভাষাগুলি মৃতপ্রায় বা মরণোন্মুখ, সেগুলির পুনরুজ্জীবন (revitalization) কি সম্ভব? আবার বলি, সেটাও নির্ভর করে ভাষার নতুন করে অর্জন করা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির উপর। সেই সঙ্গে গোষ্ঠীর ব্যাকুল আবেগ ও ইচ্ছার উপর। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইজরায়েলের হিব্রু ভাষা। ইজরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দুহাজার বছরের কিছু আগেই লুপ্ত হয়েছিল, ইহুদিরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সেই সেই দেশের ভাষা গ্রহণ করেছিল—এ ঘটনা ভাষার মৃত্যুর ধ্রুপদি ছক অনুযায়ীই ঘটেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিদের কৃপায় ১৯৪৮-এ প্যালেস্টাইনিদের জমি অধিগ্রহণ করে নতুন ইজরায়েলের পত্তন হওয়ার পরে পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানে বিত্তে ও অন্যান্য অর্জনে (ইহুদিদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে আটশো জনের বেশি) বিপুলভাবে সমৃদ্ধ প্রচুর ইহুদি ফিরে এসে ইজরায়েলে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করে। ইংরেজি, জার্মান, ইডিশ (এটি জার্মানের একটি উপভাষা), ফরাসি, রুশ ইত্যাদি ভাষী ইহুদি মানুষেরা এই নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করে যখন একটি গোষ্ঠীভাষার প্রয়োজন বোধ করল, তখন তারা কোনো একটি উপস্থিত গোষ্ঠীর অভ্যস্ত ভাষা গ্রহণ করল না, বরং নিজেদের প্রাচীন ভাষা, যা তাদের ধর্মগ্রন্থে (ওল্ড টেস্টামেন্ট, তালমুদ ইত্যাদি), ধর্মাচরণে ব্যবহৃত, সেই প্রাচীন হিব্রুকেই নতুন করে মুখের ভাষা হিসেবে বাঁচিয়ে তুলল। পৃথিবীতে এ রকম দৃষ্টান্ত আর নেই।
মনে রাখতে হবে, হিব্রুর প্রাচীন লিপি, বিপুল সাহিত্য এবং ধর্মাচরণে অব্যাহত ব্যবহার ছিল, ভাষার প্রচুর নমুনা হাতের কাছে সুলভ ছিল, আর তা ছিল বলেই এ রকম সম্ভব হয়েছে। যে ভাষা লিপিবদ্ধ নয়—পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষুদ্র ভাষাই তাই—সে ভাষার ক্ষেত্রে এ রকম সম্ভব হয় না, আর সে-সব ভাষার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তিও এমন হয় না যে, সে অন্য ভাষার মানুষদের সে ভাষা গ্রহণে আগ্রহী করে তুলবে। কারণ সেই পুরনো কথা, বৈষয়িক লাভ-লোকসানের বিবেচনা। ও ভাষা শিখে আমার কী লাভ হবে? শুধু ভাষাটি সুন্দর, বা ওই ভাষার সংগঠন সুন্দর—এমন বিবেচনায় নিজের ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষা ধরে খুব কম লোক। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে থাকে সামাজিক বিবেচনা—হয়তো অন্য ভাষার ছেলে বা মেয়ে বিয়ে করেছে কেউ। তখন কেউ সেই ভাষা শিখে দ্বিভাষী হয়, পরে তাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো মা বা বাবার ভাষায় একভাষী হয়ে ওঠে। এই সব বিবেচনার ফলেই আইরিশ বা ওয়েল্শ ভাষার পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ সফল হয় নি। প্রবল ইংরেজি দ্বিভাষিকতার ফলে ইংরেজিকে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে দুটি ভাষাই। দু-ভাষারই প্রচুর লেখক ও কবি কেবল ইংরেজিতেই লিখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।
সম্পূর্ণ মৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথম শর্ত, তার লিপি থাকতে হবে, মৃত ভাষাটি কী রকম ছিল, তার বিস্তারিত নমুনা থাকবে। এই কারণেই মরণোন্মুখ ভাষাগুলিকে লিপিবদ্ধ করার একটি প্রকল্প থাকে। এক্ষেত্রেও নানারকম গোষ্ঠীগত অভিমানের সমস্যা থাকে। একসময় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকেরা পৃথিবীর বহু ভাষা রোমক (ইঙ্গ-রোমক) লিপিতে লেখা শুরু করেছিলেন, বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন সেই সব ভাষায়। কিন্তু পরে অনেক গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের ভাষার জন্য লিপি উদ্ভাবন করেছেন, তারা সেইগুলি ব্যবহারের দিকে এগিয়ে এসেছেন।
এখানে যোগ করি, কোন লিপি আদর্শ, কোন ভাষার পক্ষে কোন লিপি যথাযথ হবে তার একটি বিজ্ঞান আছে। ফলে লিপিবিজ্ঞানের সেই সূত্রগুলি মেনে লিপি নির্মাণ করলে তা ব্যবহারের সুবিধা হয়। কিন্তু অনেক সময় বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর লিপি-উদ্ভাবকেরা লিপিবিজ্ঞানের ন্যূনতম সংবাদ না নিয়ে নিছক ভাষাপ্রেমকে সম্বল করে লিপির উদ্ভাবন করেন, ফলে সে লিপি লিখতে বেশি সময় লাগে, মুদ্রণেও অসুবিধে হয়। অনেক গোষ্ঠী ধর্মের এবং বৃহৎ ভাষার শক্তি-প্রতিফলনের কারণে পাদ্রীদের দেওয়া রোমক বর্ণমালাকেই স্বীকার করে নেন, যদিও রোমক বর্ণমালা তাদের ভাষার ধ্বনিকে যথাযথ প্রকাশিত করে না, প্রায়ই এমন দেখা যায়। তবে তারা বলতেই পারেন যে, পৃথিবীর অনেক লিপিই, ইংরেজি (ইঙ্গ-রোমক), ফরাসি, বাংলা, তামিল, আরবি ইত্যাদি—সেই সেই ভাষার সঙ্গে হুবহু খাপ খায় না অর্থাৎ সেই ভাষার ধ্বনিগুলিকে অবিকল প্রতিফলিত করে না। কাজেই তাদের লিপি, নিখুঁত না হলেও তাদের প্রিয় এবং ব্যবহার্যই থাকবে। এই আবেগের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো যুক্তি নেই। কম্পিউটারে লেখার প্রযুক্তি এসে অবশ্য হাতের লেখার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের এখনো হাতের লেখার সঙ্গেই চলতে হয় দীর্ঘদিন, সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারেও হাতের লেখা বাতিল হয়ে যায় নি।
ভাষায় লিপি যোগ করার পর দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাতে ব্যাপক ‘পাঠ’ বা টেক্সট তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি ওই সব পাঠের শ্রাব্য রূপ ধরা হবে সিডিতে, যাতে লিখিত রূপের সঙ্গে শ্রাব্য রূপ মিলিয়ে পড়া যায়। তা হলে ভাষাটি শুনতে কীরকম—তা বোঝা যাবে। শুধু শ্রাব্য রূপেরই বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে, সমস্ত ভাষাখণ্ডের লিখিত রূপ থাকুক আর না থাকুক।
এই ‘পাঠ’ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হবে ওই ভাষাটির ব্যাকরণ, তৈরি করতে হবে তার অভিন্দা গান ও কবিতার পাঠের সঙ্গে গদ্যের পাঠ মিলিয়ে গান ও কবিতার ভাষা কোথায় গদ্যভাষা থেকে আলাদা—তারও ব্যাকরণ নির্মাণ করতে হবে। অভিধানে নিজস্ব শব্দ এবং ঋণশব্দের তফাত করে শেষের উপাদানগুলির উৎস-নির্দেশ করতে হবে। ভাষাটির মৌখিক রূপের একটি মস্ত ‘শ্রুতিভাণ্ডার’ গড়ে তুলতে হবে, যে ‘অডিও আর্কাইভে’ সঞ্চিত থাকবে সে ভাষার ব্যবহারের নানা নমুনা। ভাষা ব্যবহারের উপলক্ষ ধরে। হাটে-বাজারে জিনিসপত্রের কেনাবেচা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সমাজপতিদের বৈঠক, ধর্মোপদেশনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা রিচুয়ালে ব্যবহৃত ভাষা, এমনকি ঝগড়ার ভাষাও তিন রকম রূপেই সংরক্ষিত থাকবে—লিখিত, শ্রাব্য এবং ভিডিওতে দৃশ্য-শ্রাব্য রূপে।
ভাষাটির লিখিত এবং অন্যান্য পাঠ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে তা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি ভাষার মৃত্যু তখনই এগিয়ে আসে যখন বাবা-মায়েরা আর সেই ভাষা সন্তানকে শেখান না, পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষে এই ভাষাসঞ্চার বা transmission ভাষাটির জীবনের একটি জরুরি শর্ত। সুতরাং পারবারিকভাবে মৌখিক সঞ্চার এবং স্কুলের পাঠ্য (মাধ্যম, বিষয়) হিসেবে পাঠ—এ দুইই বিশেষ জরুরি। অবশ্যই অন্যভাষীদেরও এ ভাষাটি শেখানোর ব্যবস্থা তৈরি করা দরকার, ছোটদের জন্য স্কুলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসেবে, বড়োদের জন্য ভাষাশিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে। ভাষাশিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ভাষাটিকে নিখুঁতভাবে শিখতে সাহায্য করবে। অন্যভাষীদের জন্য সে ভাষাশিক্ষার ব্যাকরণ ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ থেকে একটু আলাদা হবে, তা বলাই বাহুল্য।
ভাষাটি শেখানোর পরিকল্পনাও অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। প্রথম প্রশ্ন, ভাষাটি কত বড়? অর্থাৎ গোষ্ঠীটির আকার কী রকম? যথেষ্ট বড় ও সংহত গোষ্ঠী না হলে স্কুলে ছাত্রছাত্রী পাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা, ভাষাটি সম্বন্ধে সেই গোষ্ঠীর মনোভাব কী? এমন হতেই পারে যে, শিক্ষা বা সচেতনতার অভাবে ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের ভাষার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয়, কিংবা তারা জীবিকা আর সামাজিক অগ্রগতির জন্য নিজের ভাষা ছেড়ে দিতেও রাজি। ছোট ছোট গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটা প্রায়ই ঘটেছে এবং এখনো ঘটে।
কিন্তু ইদানীংকালে একটি শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, গোষ্ঠী তুলনায় ছোট হলেও নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং ভাষাকে ঘিরে তাদের একটি আবেগ তৈরি হচ্ছে। এই আবেগ না থাকলে শত গবেষণা আর নমুনা-সংরক্ষণ, ব্যাকরণ আর অভিধান রচনাতেও কিছু হবে না, সেগুলিতে ভাষার মৃত রূপটি ধরা থাকবে মাত্র। তারও প্রয়োজন আছে অবশ্যই, এবং পৃথিবীর অনেক ভাষা শুধু ওই বিদ্যায়তনিক জাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু ইদানীংকালে সচেতনতার বিস্তার ঘটছে, ভাষা যে গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় পরিচয়, এটা অনেকে বুঝেছেন। বিশেষত শিক্ষাবিস্তারের ফলে বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই আবেগকে আরো সমর্থন দিচ্ছেন। এর পিছনে রাজনৈতিক লক্ষ্য যে একেবারে নেই তা নয়। ভাষা সেখানে হয়ে উঠছে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের একটি অস্ত্র। ১৯৯০-এর পর থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই ভাষার মৃত্যু প্রতিরোধকামী নানা সংগঠন গড়ে উঠেছে। ২০০০ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এ বিষয়ে মানুষ আরো তীব্রভাবে সচেতন হয়েছে।
এর ‘ভালো’ আর ‘খারাপ’ দুটি দিকই আছে। অবশ্যই কে কোন পক্ষে তার উপর ‘ভালো’ বা ‘খারাপ’ সিদ্ধান্তগুলি নির্ভর করে। ভাষা-আন্দোলনের পরিণাম হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীন আবির্ভাব আমাদের কাছে ইতিবাচক ঘটনা, কিন্তু পাকিস্তানের কাছে নেতিবাচক। অর্থাৎ ভাষার স্বাধিকারকে কেউ কেউ দেশের বা অঞ্চলের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক মনে করতেই পারেন। তবে ভাষাকে ভালোবাসা ছাড়া ভাষারক্ষণের যে কোনো বিকল্প নেই সে কথাটাই সত্য। এডোয়ার্ডস (১৯৯৫ : 129) ভাষাপ্রেমের অনেক ঘোষণা আর স্লোগান উদ্ধার করেছেন, কৌতূহলী পাঠক ফিশ্ম্যানের (১৯৯৭) বইটিতে আরো বিস্তারিত সংবাদ পাবেন। ভাষাকে ভালোবাসার ওই মূল শক্তিটি না উপস্থিত থাকলে ভাষাবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ আর গবেষকদের শত চেষ্টাও ভাষাকে জীবিত রাখতে পারবে না। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিকভাবে ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন হলেও না।
সূত্রপঞ্জি
- ইসলাম, রফিকুল ও পবিত্র সরকার (সম্পা.), ২০১২ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
- সরকার, পবিত্র, ২০০৩, ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং
- ----,২০১৩, চম্স্কি, ব্যাকরণ ও বাংলা বানান, কলকাতা, পুনশ্চ।
- সিকদার, সৌরভ, ২০১২, “বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা”, দ্র. ইসলাম ও সরকার (সম্পা.), ২০১২, পৃ. ২০৩-২২৬।
- Crystal, David, 2004, The Language Revolution, Polity, Cambridge, England. Edwards, John, 1995, Multilingualism, London, Penguin.
- Fishman, Joshua A., 1997, In Praise of the Beloved Language, Berlin & New York, Mouton de Gruyter.
- Janson, Tore, 2012, The History of Languages, Oxford etc., Oxford University Press. Lightfoot, David, 2006, How New Languages Emerge, Cambridge etc., Cambridge University Press.
- Sasse, Hans Jurgen-এর প্রবন্ধ ‘Theory of Language Death’ এবং অন্যান্য কিছু তথ্য Google-সন্ধানের সূত্রে প্রাপ্ত।
- Skutnabb-Kangas, Tove, 2000, Linguistic Genocide in Education—Or Worldwide Diversity and Human Rights, Indian Reprint, Bangalore etc., Orient Longmans.