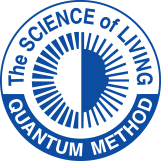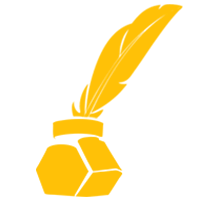কেন বিশ্বাস করব?
published : ১৪ জুন ২০১৬
আপনি নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে পারেন—কেন বিশ্বাস করব কোরআন আল্লাহর কালাম? কেন বিশ্বাস করব কোরআন মানুষের রচনা নয়? কেন বিশ্বাস করব যে, কোরআন অনুসরণ করলে আমি ভালো থাকব? কেন বিশ্বাস করব যে, কোরআন আমাকে পার্থিব জীবনেও সুখী ও প্রাচুর্যবান করতে পারে?
অবশ্যই বিশ্বাস করার আগে প্রশ্ন করতে হবে। সবদিক থেকে খতিয়ে দেখতে হবে। জানতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে। ভাবতে হবে। বিষয়ের গভীরে ডুবে যেতে হবে। বিচার করতে হবে মুক্তমন নিয়ে, বস্তুনিষ্ঠভাবে। তাহলেই আপনি সত্যে উপনীত হতে পারবেন।
ইতিহাসের দিকে তাকান :
- একজন মানুষ—যাঁর শুরুটাই শূন্য। পৃথিবীর আলোর মুখ দেখার আগেই পিতৃহারা। ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা। আট বছর বয়সে আশ্রয়দাতা পিতামহকে হারান। এরপর চাচার কাছে লালিত। পড়াশোনার সুযোগবঞ্চিত কৈশোর কেটেছে মরুভূমিতে মেষ চরিয়ে।
- একজন মানুষ—যিনি নিরক্ষর ছিলেন। পড়তে বা লিখতে পারতেন না।
- একজন মানুষ—যিনি কখনো কোনো কবিতা লেখেন নি। কোথাও ভাষণ দেন নি। কোথাও ওয়াজ করেন নি। কবি, বাগ্মী বা ধর্মবেত্তা হিসেবে যাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না।
- একজন মানুষ—দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, মহাকাশবিজ্ঞানী হিসেবেও যিনি খ্যাতিমান হন নি।
- একজন মানুষ—যিনি ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সদাচারী ভালো মানুষরূপে, একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে, একজন সত্যবাদী মানুষরূপে।
৪০ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুরু করল জীবনের বাঁকবদলকারী বাণীমালা, যা আরবি ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত। তিনি বললেন, আল্লাহ এই বাণীমালা তাঁর ওপর নাজিল করেছেন। আরবি ভাষার সকল কবি-সাহিত্যিক স্বীকার করলেন, না, এর মতো কোনো পঙক্তিমালা তাদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল কিন্তু এর মতো কোনো পঙক্তিমালা কারো পক্ষেই রচনা করা সম্ভব হলো না।
আপনি বলতে পারেন, কালজয়ী কবি সাহিত্যিকরাও অনন্য সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন এবং তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তাই কোরআন যত অনন্যই হোক না কেন, তা মানুষের রচনা নয় এটা নিশ্চিত হবো কীভাবে? আসলে কালজয়ী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের অনন্যতা এবং কোরআনের অনন্যতার ধরনে মনোনিবেশ করলেই বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।
১. কালজয়ী কাব্য বা সাহিত্য যে আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে, সে আঙ্গিকটা অনন্য নয়। সেই ছন্দ বা সেই আঙ্গিকে আরো অনেকেই কাব্য বা সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু কোরআন আরবি সাহিত্যের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অতুলনীয় এক আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। এই আঙ্গিকে এর আগে বা এর পরে কোনো সাহিত্য-প্রয়াসই চালানো সম্ভব হয় নি।
২. সকল কালজয়ী সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষের জন্যে শব্দের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন সাহিত্যিক বা কবি নিজেই করেছেন। কিন্তু কোরআনের সাহিত্যিক অনন্যতা, এর অতুলনীয় মাধুর্য, ছন্দ ও শব্দবিন্যাস সত্ত্বেও তা তৎক্ষণাৎই বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্যে পরবর্তীতে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয় নি।
৩. যে-কোনো কাব্য, সাহিত্য বা শিল্পকর্মে রচয়িতার আবেগ, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মনের দুঃখকষ্টের প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু কোরআন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দুঃখের প্রসঙ্গ বা প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি তাঁর যৌবনের ২৫ বছর যে নারীর সাথে কাটিয়েছেন, তাঁর সেই প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা) মারা যান অর্ধাহারে-অনাহারে, কোরাইশদের হাতে সঙ্গীসাথিসহ পাহাড়ের পাদদেশে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায়। ২৫ বছরের প্রেম, যত্ন, সহযোগিতা সব ছেড়ে চলে গেলেন, যাঁর প্রতি নবীজী (স) ছিলেন আজীবন বিশ্বস্ত, অনুরক্ত। যিনি ছিলেন তাঁর নবুয়তের ওপর আস্থা প্রকাশকারী প্রথম ব্যক্তি, যিনি ছিলেন তাঁর আট সন্তানের মধ্যে সাত সন্তানের জননী, যিনি ছিলেন তাঁর সাধনার সহযোগী, চেতনা বিস্তারের সংগ্রামে সহযোদ্ধা। যিনি সকল সম্পদ উজাড় করে দেন তাঁর জন্যে, যিনি নিজের গোত্রীয় মর্যাদা ও সম্পর্কচ্ছেদ করেন তাঁর জন্যে, তিনি চলে গেলেন মর্মন্তুদ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু এসবের কোনো ধরনের উল্লেখ কোরআনে নেই। কোনো কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর জীবন থেকে যদি এমন জীবনসঙ্গিনী হারিয়ে যেতেন, তাহলে কী পরিমাণ কাব্য, সাহিত্য, গান রচিত হতো তা যে-কেউই অনুমান করতে পারেন। অথচ কোরআনে হযরত ইব্রাহিম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত লূত (আ) এবং ফেরাউনের স্ত্রীর কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর স্ত্রী খাদিজার (রা) কোনো উল্লেখ নেই। কোরআনে নাম উল্লেখ করে একমাত্র যে নারীর কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন বনি ইসরাইলি নবী হযরত ঈসার (আ) মাতা বিবি মরিয়ম। মনুষ্য রচনা নয়, শুধু ঐশীবাণী হলেই এমনটি সম্ভব।
৪. হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর চোখের সামনে চারটি ছেলের প্রত্যেকের মৃত্যু দেখেছেন। তাঁর চার মেয়ের তিন জনই তাঁর জীবদ্দশায় মারা যান। তাঁর প্রিয়তম চাচা হামজা-র লাশের সাথে পাশবিক আচরণ, তাঁর সাথিদের ওপর ক্রমাগত লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন এমনকি অনেককে হত্যা করা হয়। তাঁর ওপরও চালানো হয় শারীরিক-মানসিক নির্যাতন। একবার তিনি যখন কাবা ঘরের সামনে সেজদারত অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর ওপর উটের পচা নাড়িভুঁড়ি স্তূপাকারে ফেলা হয়। পরিমাণ এতটাই ছিল যে, তাঁর শরীর মাটির সঙ্গে লেগে যায়। তাঁর কন্যা তাঁর শরীরের ওপর থেকে পচা নাড়িভুঁড়ি না সরানো পর্যন্ত তিনি মাথাই তুলতে পারেন নি। একবার কল্পনা করুন, গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে পচা নাড়িভুঁড়ির স্তূপ ফেলা হলো আপনার শরীরের ওপর, আর তা থেকে নিঃসৃত রস আপনার ঘাড়ে, কাঁধে, কানের দুপাশ দিয়ে নাকে, ঠোঁটের দিকে গড়িয়ে আসছে! পচা নাড়িভুঁড়ির উৎকট দুর্গন্ধের কথা বাদ দিলেও কতটা বিরক্তিকর স্নায়ু-উত্তেজক বিষয় হতে পারে এটা! এরকম ঘটনা কারো স্মৃতিকে বিষণ্ন বিরক্ত না করে পারে না। অথচ এর কোনো উল্লেখ কোরআনে পাওয়া যায় না।
কোরআনে রসুল (স)-এর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রতিফলনের পরিবর্তে কোথাও কোথাও তাঁর চিন্তাকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। যখন রসুল (স) আগ্রহী অন্ধ বৃদ্ধের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন সূরা আবাসায় তাঁর এ-কাজটি যে উচিত হয় নি, তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। রসুল (স) যখন স্ত্রীদের মনরক্ষা করার জন্যে মধু না খাওয়ার শপথ করেছিলেন, তখন সূরা তাহরিমের প্রথম আয়াতে তা সংশোধন করে নিতে বলা হয়। রসুলের (স) দু-একটা ছোটখাটো মানবীয় ত্রুটিকেও কোরআন সংশোধন করে দিয়েছে, যেন এ-কাজটা আল্লাহ-অনুমোদিত কাজ হিসেবে প্রচলিত না হয়ে যায়। যদি কোরআন মানবরচিত হতো, তবে রচনাকারী তার ভুলকে কখনোই প্রকাশ্যে আনতেন না। বরং তিনি যে কত সঠিক, আয়াতে আয়াতে তা-ই প্রমাণ করার চেষ্টা হতো।
শুধু এ কালের সংশয়ীরাই নয়, রসুল-যুগের সংশয়ীরাও প্রথমে বলার চেষ্টা করেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স) কোরআনের রচয়িতা। এর জবাবে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জ দেন, কোরআনের সূরার মতো ১০টি সূরা রচনা করে আনার জন্যে : ‘ওরা কী বলছে? কোরআন তুমি রচনা করেছ? (হে নবী!) ওদের বলো, যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে তোমরা এ ধরনের ১০টি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো সাহায্যের জন্যে ডাকো। যাদেরকে ডাকছ তারা যদি তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম না হয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকেই এ কোরআন নাজিল হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এরপরও কি তোমরা তাঁর কাছে সমর্পিত হবে না?’ (সূরা হুদ : ১৩-১৪)
কিন্তু যখন তারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহ ১০টির জায়গায় শুধু একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে বলেন : ‘আমি আমার বান্দার প্রতি ধাপে ধাপে যা নাজিল করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে এর মতো একটিমাত্র সূরা রচনা করো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীকে ডাকো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে একটি সূরা এনে দেখাও। আর যদি তা না পারো এবং তা তোমরা কখনোই পারবে না, তাহলে সচেতন হও জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।’ (সূরা বাকারা : ২৩-২৪)
সবশেষে আল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সত্য অস্বীকারকারীদের চূড়ান্ত ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী করেন : ‘(হে নবী! ওদের) বলো, পৃথিবীর সকল মানুষ ও জ্বীন যদি একযোগে সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালায়, তবুও এ কোরআনের মতো আরেকটি কোরআন আনতে পারবে না।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ৮৮)
প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ কিছু মোজেজা দেখানোর সামর্থ্য দিয়েছেন; যা সে-স্থান ও কালেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে-সময় যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে শুধু তারাই বিষয়টি অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছে। আর রসুল (স)-এর প্রতি নাজিল করা কোরআন নিজেই এক মোজেজা অর্থাৎ অলৌকিক নিদর্শন; যার একটি সূরার মতো সূরা আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারে নি এবং কোনোদিনই তা পারবে না। আর এ অলৌকিক নিদর্শন সগৌরবে মূল ভাষায় পূর্ণাঙ্গরূপে বিরাজ করবে কেয়ামত পর্যন্ত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনন্তকাল ধরে এ থেকে লাভ করবে সঠিক জীবনদৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রাচুর্য ও কল্যাণ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যে ধন্য হবে তাদের জীবন।
॥ ২ ॥
‘বিশ্বাস’ প্রসঙ্গটি আমরা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পারি। আমরা সবাই কিছু না কিছু বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস হতে পারে কোনো ধারণায়, কোনো মতবাদে, কোনো ব্যক্তিমানুষে। আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে কখনো কোনো ব্যক্তির বক্তব্য শুনে বা চারপাশের মানুষের খণ্ড খণ্ড কথা শুনে, তাদের আচার-আচরণ দেখে।
বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিশ্বাসের প্রকৃতি ইতিবাচক। আর অবিশ্বাসের প্রকৃতি নেতিবাচক। একটা হাঁ। আরেকটা না। ‘আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি’—এটা হলো ইতিবাচক বিশ্বাস। ‘আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না’ —এটাও একটা বিশ্বাস—তবে নেতিবাচক বিশ্বাস। এটাই হলো অবিশ্বাস, অর্থাৎ বিশ্বাসের অপর পিঠ। এ-ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই তৃতীয় একটা শব্দ শুনি। সেটি হলো সংশয়। আসলে নিজের সহজাত বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আস্থাহীনতার প্রকাশই হচ্ছে সংশয়। সংশয় বা সন্দেহপ্রবণতা আসলে একটি মনোরোগ।
আমাদের বিশ্বাসের শিকড় রয়েছে ডিএনএ-রই গভীরে। তাই প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করে। কেউ স্রষ্টায় বিশ্বাস করে, কেউ করে শয়তানে, কেউ ভালো মানুষে বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে প্রতারকে, কেউ বিশ্বাস করে সাধুকে, কেউ বিশ্বাস করে ভণ্ডকে। কেউ দেখে অন্তর, কেউ দেখে চাকচিক্য। কেউ দেখে সারল্য, কেউ দেখে জৌলুস। তাই আপনার বিশ্বাসের ভিত্তিটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভিত্তি মজবুত হয়, আপনি তার ওপর প্রাসাদ গড়তে পারবেন। আর যদি তা হয় চোরাবালি, আপনি অতলে তলিয়ে যাবেন। আর বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যর্থ হতাশ শোষিত বঞ্চিতরা সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে, বাস্তবতার পরিবর্তে অলীক কল্পনাকে, সরল সত্যবাদীর পরিবর্তে ধূর্ত বাক্যবাগীশকে, নিখাদ সত্যবাণীর পরিবর্তে শ্রুতিমধুর বাগাড়ম্বরকে বিশ্বাস করে। নির্বোধরা নিজের দায়িত্ব নিজে না নিয়ে অন্যের ওপর ছেড়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ কারণেই তারা প্রতারিত হয়, দুর্দশায় হাবুডুবু খায়।
এখন আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। আপনি কাকে বিশ্বাস করবেন—সত্য না মিথ্যাকে, সদাচারীকে না দুরাচারীকে, সেবককে না শোষককে, উপকারীকে না প্রতারককে? আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে সাফল্যের সরলপথে চলবেন, না অন্যের ওপর নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে দুর্দশায় হাবুডুবু খাবেন?
ইতিহাসের দিকে তাকান। আরব। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ। অবিদ্যা, অনাচার আর অত্যাচার, হিংসা ও হানাহানিতে নিমজ্জিত এক সমাজ। যেখানে নিজের কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেয়ার মতো নৃশংসতা ছিল পৌরুষের প্রতীক, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মুহাম্মদ (স)। পিতৃমাতৃহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে একজন সৎ ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যবাদী হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল সর্বজনবিদিত। সদা সত্যবাদিতার জন্যে তাঁকে আল-আমিন অভিধায় ভূষিত করা হয়।
মানুষের দুঃখ, সামাজিক অনাচার, জুলুম, বঞ্চনা ও নৃশংসতা তাঁকে ব্যথিত করে। এ থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে তিনি নগর থেকে দূরে হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন হতে শুরু করলেন। প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি সেখানে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকালে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে তাঁর কাছে জিবরাইল (আ)-এর আগমন ঘটে। ঘটনার বর্ণনায় নবীজী (স) বলেন, ‘জিবরাইল বলল, পড়ো!’ আমি জবাবে বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না।’ তখন জিবরাইল আমাকে জাপটে বুকে চেপে ধরলে আমার মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। আবার বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না।’ এইভাবে তিন বার বুকে চেপে ধরার পর আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘কী পড়ব?’ তখন জিবরাইল বলল, ‘পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ো! তোমার প্রতিপালক মহান দয়ালু। তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।’
আমি পড়লাম। জিবরাইল আমাকে ছেড়ে চলে গেল।
নবীজী (স) বলেন, ‘উস্কোখুস্কো কবিদের আমার মোটেই পছন্দ না। আমার মনে হলো, কোরাইশরা সব শুনলে আমাকে ওদের (কবিদের) দলেই ফেলে দেবে। নানা ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আমি পাহাড়ের ওপরদিকে উঠতে শুরু করলাম। হঠাৎ ওপর থেকে শুনি শব্দ ভেসে আসছে—‘আমি জিবরাইল। মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসুল।’ আমি ওপরদিকে তাকালাম, আমি জিবরাইলকে দেখলাম মানুষের রূপে—পা মাটিতে আর দেহ দিগন্তবিস্তৃত। সে আবার বলল, ‘মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসুল। আর আমি জিবরাইল।’ আমি স্থাণুর মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। নড়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু যেদিকে তাকাই দিগন্তবিস্তৃত তাকেই দেখতে পাই। একসময় সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। আমি ঘরে ফিরে এলাম।’
হযরত মুহাম্মদ (স) গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে এলেন। স্ত্রী খাদিজাকে (রা) বললেন, ‘আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।’ তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। কাঁপুনি থেমে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় এলে তিনি বিস্ময়ের সাথে খাদিজাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার কী হয়েছে?’ পুরো ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে তিনি বললেন, ‘আমার ভয় হচ্ছে।’ খাদিজা (রা) উত্তরে বললেন, ‘আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি বিশ্রাম নিন। আল্লাহ আপনার কোনো অমঙ্গল করতে পারেন না। কারণ আপনি সত্যবাদী, দানশীল, অতিথিপরায়ণ ও ভালো কাজে এবং অন্যের প্রয়োজনে সাহায্যকারী। আপনি ঠিক দেখেছেন। আমি বিশ্বাস করছি, আপনি আল্লাহর রসুল।’
এরপর খাদিজা (রা) নবীজীকে (স) নিয়ে মক্কায় বসবাসকারী তখনকার বিশিষ্ট খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওরাকা বিন নওফেলের কাছে যান। সব কথা শুনে বর্ষীয়ান ওরাকা বললেন, ‘এই বাণীই মুসার ওপর নাজিল হয়েছিল। বড় ইচ্ছা হয়, আমি যদি তরুণ হতাম তাহলে এই নগরের অধিবাসীরা যখন তোমাকে নগর থেকে বের করে দেবে, তখন আমি তোমার পাশে থাকতাম।’
নবীজী (স) বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘নগরবাসীরা আমাকে বের করে দেবে কেন?’ ওরাকা বললেন, ‘আসলে শত্রুতার মুখোমুখি না হয়ে কোনো নবীই সত্যবাণী প্রচার করতে পারে নি। আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি আমি অবশ্যই তোমাকে সমর্থন করব।’ কিন্তু কিছুদিন পরই ওরাকা মারা যান।
আসলে একজন মানুষ কতটা আন্তরিক ও নিজের কাছে সৎ হলে হেরা পাহাড়ের ঘটনা এত অকপটে বলতে পারেন! বিষয়টি তাঁর কাছেই কত অপ্রত্যাশিত ছিল এবং তিনি কতটা শঙ্কিত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তা ঘটনার বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। (যদি কেউ নিজেকে নবী ঘোষণার জন্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কাজ করত, তবে তার নবুয়ত লাভের কল্পিত ঘটনায় নিজের মহত্ত্বকেই নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। নিজের মানবীয় দুর্বলতার কথা কখনোই প্রকাশ পেতে দিত না।) আর একজন মানুষ স্ত্রীর কাছে কতটা সৎ ও বিশ্বস্ত থাকলে ১৫ বছর একসাথে ঘর করার পর একমুহূর্ত দ্বিধা না করে স্ত্রী বলতে পারেন যে, ‘আমি বিশ্বাস করছি আপনি আল্লাহর রসুল’, তা-ও আমরা আঁচ করতে পারি।
এই সৎ ও সত্যবাদিতা ঘরে-বাইরে কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা-ও আমরা বুঝতে পারি এর তিন বছর পরের একটি ঘটনা থেকে। তিন বছর ধরে তিনি সংগোপনে নতুন বিশ্বাসের কথা প্রচার করে আসছিলেন। এরপর তিনি আদিষ্ট হলেন প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে। তাই তিনি মক্কার কেন্দ্রে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে তাদের পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানালেন। শহরে দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেয়ার জন্যে মুহাম্মদ সবাইকে ডেকেছেন। শহরের চারদিক থেকে লোকজন দ্রুত এসে সেখানে সমবেত হলো। সবাই সমবেত হওয়ার পর নবীজী (স) তাদের সামনে প্রশ্ন রাখলেন, ‘যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের ওপারে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী মক্কা আক্রমণের জন্যে সমবেত হয়েছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই একবাক্যে জবাব দিল, ‘অবশ্যই। কারণ আপনি সত্যবাদী, কখনো আপনাকে আমরা মিথ্যা বলতে শুনি নি।’ রসুলের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য একসাথে দেয়ার পরও তিনি যখন আল্লাহর নির্দেশের কথা বললেন, তখন বদমেজাজী ধনাঢ্য বিলাসী ব্যবসায়ী আবু লাহাব চিৎকার করে উঠল, ‘তোমার বিনাশ হোক! এই উদ্ভট বিষয় শোনাতে তুমি আমাদের ডেকেছ!’ সমবেত সাধারণ কোরাইশরা শোষক আবু লাহাবের পক্ষ নিয়ে রসুলকে প্রত্যাখ্যান করে গালিগালাজ করতে করতে চলে গেল। রসুল (স) কিছুক্ষণ পর দেখলেন পাহাড়ে তিনি একাই দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝলেন আসন্ন সময় হবে কত কঠিন!
সংশয়ী মন এখানেও প্রশ্ন করতে পারে, হাঁ, তিনি সত্যবাদী ছিলেন, ঠিক আছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তিনি তো মিথ্যাও বলতে পারেন?
এর উত্তর খুব সহজ। একজন পুরুষ মানুষ সাধারণত পাঁচটি কারণে মিথ্যা বলতে পারে। ১. মিথ্যা বলাটাই তার স্বভাব। ২. অর্থের জন্যে। ৩. ক্ষমতার জন্যে। ৪. নারীর জন্যে। ৫. জীবন বাঁচানোর জন্যে।
প্রথম কারণটা নবীজীর (স) বেলায় পুরোপুরিই অনুপস্থিত। কারণ তিনি কখনো মিথ্যা বলেন নি। তিনি সমাজে আল-আমিন অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই আমরা বলতে পারি, কোরআনের বাণী প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্যে কোরাইশ নেতারা সম্মিলিতভাবে তাঁকে প্রকাশ্য প্রস্তাব দিয়েছিল—যত অর্থ চাও আমরা তোমাকে দেবো, নেতৃত্ব চাও তোমাকে নেতা বানাব, যদি রাজত্ব চাও তোমাকে রাজা বানাব, তুমি শুধু তোমার বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকো। নবীজী (স) বলেছিলেন, যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চন্দ্র এনে দাও, তবুও আমি সত্যবাণী প্রচার থেকে বিরত হবো না। তাহলে আমরা দেখছি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণও এ-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। চতুর্থ কারণ প্রসঙ্গে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি, স্ত্রী বিবি খাদিজাই ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর জীবনে সবচেয়ে প্রিয় নারী। পরবর্তী জীবনে অন্য সকল বিয়েই ছিল বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পূরণের প্রয়াস। আর পঞ্চম কারণও তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং বলা যায়, কোরআনের বাণী প্রচারের জন্যে তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন বার বার।
প্রশ্ন করতে পারেন, কেন তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে গেলেন? তিনি তো খেয়েপরে ব্যবসাবাণিজ্য ঘরসংসার নিয়ে প্রাচুর্যের মধ্যেই ছিলেন। তারপরও তিনি কেন নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে গেলেন?
উত্তর একটাই। তা হলো, মানুষের দুঃখদুর্দশা শোষণবঞ্চনার অবসানের জন্যে। নিপীড়িত লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের মুক্তির জন্যে। অবহেলা-অপমানে জর্জরিত নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। দুর্ভাগ্যকে নিয়তির লিখন ভেবে স্বনির্মিত শৃঙ্খলে বন্দি মানুষকে মুক্ত করে তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের জন্যে। মানুষকে পৃথিবীতে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন করার জন্যে। এককথায় মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিত্রাণের জন্যে।
নবীজীর (স) নবুয়ত-পরবর্তী ২৩ বছরের জীবন আশাহত সাধারণ মানুষকেও ধ্যানী, জ্ঞানী, কর্মী ও অভিযাত্রীতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রাণান্ত প্রয়াসের জীবন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অনুসারীদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন, গভীর রাতে আল্লাহর ধ্যান ও ইবাদতে নিজেকে নিমগ্ন রাখা আর প্রতিটি কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য কাজে নিজে মাঠে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার জীবন। ছোটবেলায় লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত একজন নিরক্ষর মানুষের জীবনও যে কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে, তাঁর জীবনই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি একাধারে সংসারী, ব্যবসায়ী, সেবক, ধর্মপ্রচারক, প্রাজ্ঞ শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, কূটনীতিবিদ, বিচারক, সেনানায়ক এবং রাষ্ট্রনায়ক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত। ফলে তিনি এমন এক চেতনার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, যা মধ্যযুগে সৃষ্টি করেছিল এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা।
তিনি শুধু স্রষ্টাপ্রেমিক ছিলেন না, ছিলেন সৃষ্টির অকৃত্রিম প্রেমিক। সৃষ্টির অধিকারকে তিনি সবার জন্যে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নদনদী, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, পশু-প্রাণীও এই সংজ্ঞা থেকে বাদ যায় নি। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে তিনি প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করেছেন। প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে নারী যাপন করত মানবেতর জীবন, সেই নারীকে তিনি প্রথম দিয়েছেন কুমারী-নামে পরিচিত হওয়ার অধিকার। দিয়েছেন জ্ঞানার্জন ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার, একা নির্বিঘ্নে চলার অধিকার, নিজস্ব উপার্জন, স্বাধীন পেশা এমনকি সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অধিকার, বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রদান এবং প্রয়োজনে তালাক দানের অধিকার। তিনি জীবদ্দশায় নারীর পরিপূর্ণ মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।
কোরআন যে আল্লাহর কালাম তা বিশ্বাস করার জন্যে এ সত্যটুকুই যথেষ্ট যে, যাঁর মুখ থেকে এই পবিত্রবাণী নিঃসৃত হয়েছে—তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তিনি মজলুমের সমব্যথী ছিলেন। আর তিনি শুধু নিজের ধর্মই প্রচার করেন নি। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে (‘মদিনা সনদ’-এ) প্রত্যেক ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছেন। মানবজাতির ইতিহাসে তিনিই ছিলেন মানবাধিকারের প্রথম সার্থক রূপকার।